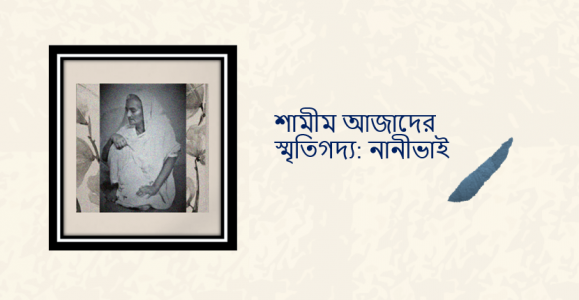আমার নানীর বিয়ে হয় ন’বছর বয়সে! শুনেছি শাশুড়িকে পাননি তিনি। শ্বশুরই তাঁকে মাতৃস্নেহে বড় করেছেন, শাড়ি পরা শিখেছেন, পড়িয়েছেন। হয়ত সে কারণেই আমাদের সমাজের পুরুষদের মতই ছিল তার আত্ম নির্ভরতা ও প্রতিপত্তি। আমরা তাকে একটু ভয়ই পেতাম। সৈয়দা কমরুন্নেছা খাতুন যখন বই থেকে মুখ তুলে তাঁর সোনালী রিমের চশমার ভেতর দিয়ে আমাদের দিকে তাকাতেন, বুঝতাম যাচন দারের হাতে পড়ে গেছি। তাঁর জামরুলের মত ফর্সা গায়ে রাঙা মুখে রাগ জমে উঠতো, আর আমরা তটস্থ হয়ে পড়তাম কখন পশ্চাতে তাল পাখার বারি পড়ে! তাঁর পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যার সূত্রে পাওয়া নাতি নাতনীদের মধ্যে কন্যার দিকের আমরা তাকে নানীভাই ডাকতাম। মামাতো ভাইবোনরা ডাকতো দাদুভাই। এমন উভয় লিঙ্গীয় সম্বোধন এর উৎস জানি না। তার সঙ্গে এ ডাক মানিয়ে যেত। আমার ভাল লাগতো তার স্মার্টনেস।
আমাদের নানীবাড়ী মৌলভীবাজারে-কনকপুরে। সামনে সাগরের মত বিশাল পুকুর পাড়, ভূতুরে তেঁতুল গাছ। গ্রামে যে তাঁর অনেক প্রতিপত্তি তা তাঁর কাছে আসা লোকজন দেখেই টের পেতাম। এ হেন ডাকসাইটে নারী বার্ধক্যে বাধ্য হয়ে পালাক্রমে সন্তানদের কাছে থাকতে শুরু করলে তাকে ঘনিষ্ঠভাবে পাই আর আমি ঐ ছ’সাত বছরেই বুঝে যাই তিনি সবাইকে ঘিরে প্রদক্ষিণ করলেও তিনি তারা না উপগ্রহ না তিনিই সূর্য।
নানা গোলাম ইয়াজদানী খান ব্রিটিশ আমলে মৌলভীবাজারের মিউনিসিপালটির চেয়ারম্যান থাকার সময় দেশ বিভাগের পর দেহত্যাগ করেন। নানীভাই ছিলেন মৌলভীবাজার মহিলা মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট। তিনি কবিতা লিখতেন। আজাদ ও কোলকাতার কোন একটা কাগজে যেন আসামের লাইন প্রথা আন্দোলনে যুক্ত থাকার সময় তাঁর লেখাও উঠেছিলো।
এই নানীই নানার প্রয়াণে রঙিন শাড়ি, গয়না সব ত্যাগ করে তুলে নিয়েছিলেন সুতা পাড় ধুতি ও ঢিলা হাতা সাদা ব্লাউজ। এবং দোর্দণ্ড প্রতাপে তারপরও বেঁচেছিলেন দুই দশকের বেশি।
তাঁর বইপড়া রোগ আমাকে আকৃষ্ট করেছিলো। আমার বয়স তখন সাত হবে। আমরা ফেনীতে ছিলাম। হাজারির পুকুর পাড়ে মাস্টার পাড়ার গোফরান সাহেবের বাড়িতে আমরা ভাড়া থাকতাম। স্কুল থেকে ফিরে দেখতাম তাল পাখা খানা এলায়ে পড়েছে, চোখে সোনালী রিমের চশমা কিন্তু চোখ বন্ধ আর পাশে পড়ে আছে গল্পের বই। জীবনের শেষ বেলায় পড়তেন বড় বড় অক্ষরে ছাপা বই। সে সব বইয়ের সরবরাহ কোথা থেকে হত জানি না।
মনে পড়ে তার একেবারে শেষ সময়ের কথা। আমার বয়স তখন সতর। আমি টাঙাইল কুমুদিনী কলেজের উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্রী। আম্মারা তখন নারায়ণগঞ্জে। ছুটিতে এসে শুনি নানীভাই মিটফোর্ড হাসপাতালে। তিনি ভীষণ অসুস্থ বলে কাউকে না কাউকে নানীভাইর কাছে থাকতে হতো। মেজমামার পুত্র বাবলু ভাই ও তাঁর মেজ কন্যার কন্যা আমি মিলে পালাক্রমে তাঁর সন্তানদের হয়ে ডিউটি দিয়েছি ক’দিন। তখন সকাল বেলা ওষুধ পথ্যাদির পর তাঁরই নির্দেশে আমরা তাঁকে প্রায় কুস্তি করে বিছানা থেকে উঠিয়ে নদী মুখো করে চেয়ারে বসাতাম। তারপর সেদিনের পত্রিকা বা বেগম পড়তাম। তিনি বুড়িগঙ্গায় ভেসে যাওয়া পালের উপরটা দেখতে দেখতে ও পড়া শুনতে শুনতে তিনি ঘুমিয়ে পরতেন। আমরা পালা করে তাকে আজাদ পত্রিকা ও মীর মোশাররফ হোসেনের বিষাদ সিন্ধু পড়ে শোনাতাম। মোহাম্মদ নজিবুর রহমান সাহিত্য রত্নের বই তাঁর পছন্দ ছিল। সে কারণেই হয়তো আমার মা ও খালামনির নাম ছিলো আনোয়ারা ও মনোয়ারা।
নানীভাইর ধুতিশাড়ি গোলা সাবানে সেদ্ধ করে ধোয়া হত। শুকোলে তা দেখা যেত কার্পাসের মত আর তা থেকে ক্ষারের সুগন্ধ আসত। ঐ বাহুল্য বিহীন শাড়িই এত সুন্দর ও কোমল করে তিনি পরতেন যে তাকে আমার রানীমাতা মনে হত।বহুদিন আমার ধারণা ছিল চাঁদের বুড়ির চরকার সুতো আর আমা র নানীভাইর কাপড়ের সুতো হুবহু এক। কিন্তু তাঁকে জড়িয়ে ধরে নাক ডুবিয়ে যখন তাঁর ঘ্রাণ নিতাম সে ছিল একদম আলাদা। তা ছিল নানান ঘ্রাণের ককটেল। চুলে দেয়ার কদুর তেল, ব্রহ্ম-তালুর ভরন, মিষ্টি জর্দার মিশেল এক সুগন্ধের এক ককটেল।
উচ্চ রক্তচাপ হলেই তাঁর মেজাজ চড়তো- আমরা বলতাম, নানীভাইর প্রেসার অইছে, আর দূরে দূরে থাকতাম। আম্মা আর্দালি ভাইকে দিয়ে নালার পাড় থেকে কাউয়ালুলীর নরম ও পিচ্ছিল পাতা আনিয়ে বেটে নানীভাইর মাথায় গোল ঢিবি করে ভরন দিয়ে দিতেন! তাঁর ডায়াবেটিসও ছিলো। রাতে ভাতের বদলে হাতেগড়া রুটি দিতে হত। সে সময় বিস্কিট মাত্রেই মিষ্টি বিস্কুট বোঝাতো। কিন্তু তাঁর জন্য মজুত থাকতো ঢাকা থেকে আনা সুগন্ধি কালিজিরা দেয়া নোনতা বিস্কুট। ভোররাতে সেই বিস্কুটের সুগন্ধে আমার ঘুম ভেঙে গেলে আধখোলা চোখে মশারির বাইরে বেরিয়ে আসতাম। দেখতাম, তিনি ফ্লাস্কের চা’তে ভিজিয়ে ঐ বিশেষ বিস্কুট খাচ্ছেন। এর সরবরাহ সীমাবদ্ধ বলে তা আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা হত। কিন্তু ভোররাতে ঠিক চা খাবার সময়ই আমি তার গা ঘেঁষে বসে বাহুর নিচের লুতলুতা অংশে আদর করা শুরু করতাম। নানীভাই তখন তার চা’ পান শেষে নিয়মিত তলানির চেয়ে একটু বেশী রেখে পিরিচে সে নোনতা বিস্কুটের ভগ্নাংশ দিয়ে বলতেন, খাই লা। হোমিওপ্যাথির গুল্লির মত দেখতে বিলেতি স্যাকারিন দিয়ে তৈরি মিষ্টি সে ঘন সরপড়া চা’কে অমৃতের বাড়া মনে হতো। আমি তার পালঙ্কে বসে পা দুলিয়ে দুলিয়ে বিস্কুট ডুবিয়ে ঐ অতটুকু চা শেষ করতে অনেক সময় নিতাম। তিনি আরেকটি মজার জিনিষ খেতেন। তা হল রুটি বানানোর বেলুন পিড়িতে পেষা ভাজা চীনা বাদাম। যাকে আমরা এখন পিনাট বাটার বলি। ধারনা করি আমার বিলেতি মামারা এই পিনাট বাটারই তাঁর জন্য কিনে এনে খাইয়েছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশে তো তখন তা পাওয়া যেত না। নানীভাইর জন্য তাই চীনে বাদাম ভেজে তা রুটি বেলার বেলুন পিড়িতে বেটে দেয়া হত। আমি বসে থাকতাম বেলুন চাটার জন্য। তিনি সেখানেও আমার জন্য একটু রাখতেন। এর সবই হতো আম্মাকে লুকিয়ে।
শীতকালে তিনি তার প্রিয় সন্তান মেজমামার পটিয়ার বাড়িতে থাকতেন। মামা তখন সেখানের মহকুমা পুলিশ প্রধান। বাড়ির সামনে বিস্তীর্ণ মাঠ আর পেছনে খেতের পর খেত আখ আর বরই। আর তারপরেই গভীর বন। শুনলাম, দুষ্টুমি করলে ওখান থেকে বাঘ আসে। আমরা ছাড়াও সে সময় বিভিন্ন স্থান থেকে আসতেন খালা ও মামারা। দুপুরের খবর পর বডি বিল্ডার সোনা মামা গুলাইল হাতে আমাদের সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে পরতেন। পথে পথে গাছের গুঁড়িতে বসে আমরা ইচ্ছে মত আখ আর কোঁচড় ভরে বরই খেতাম।বাড়ি ফিরে দেখতাম নানীভাই পাটালি গুড় দিয়ে বিচিত্র আকারের মুড়ির মোয়া করে রেখেছেন! এদের নামও দিতেন। কোনটা পাটা, কোনটাকে পুঁতা, কোনটা লাড্ডু, কোনটা বটলা ও কোনটা পেটলা। রাতে কষা বরই খাওয়া জিবের জ্বালা নিয়েও গুড়ের লালি, পুরু সরপরা দুধ আর ভাত খেতাম। তখন সারা বাড়ি খেজুর গুড়ের সুগন্ধে ম ম করতো। রাতে বুজে শুনতে পেতাম বাঘের ডাক। নানাভাই তখন দোয়া শিখিয়ে দিলে সেটা পরে বুকে ফু দিয়ে আবার ঘুমোতে যেতাম।
আমার মা ঠিক নানীভাইর মত গুনগুন করে গান গাইতেন। কিন্তু তিনি যে ভালই গান সেটা জানার সুযোগ হল আমার বয়স এগারো বা বারো’র সময়। ঐ সোনা মামার একটা মজার জায়গায় চাকুরী করতেন ও পরিবার নিয়ে থাকতেন। মেঘনার উপর ছোট্ট দারুচিনি দ্বীপ মার্কা দ্বীপ-বাংলাতে বিলেত প্রবাসী মায়ামামার বিয়ে লাগলে আমরা সেখানে গেলাম। বিয়ে উপলক্ষে এলেন ওঁর তিন বোন, আর পড়লো গানের ধুম। সিলেটের আউশপাড়া, চন্দ্রচড়ি ও স্নান ঘাট থেকে এসেছিলেন তিন বিধবা।
হলুদের দিন যখন সাদা সাদা থানপরা চার নানী লাইন ধরে তাঁদের সুন্দর সোনালী পানের বাটা সামনে নিয়ে যখন গান ধরেছিলেন, আমার তাদের সাদা সাদা পরী মনে হচ্ছিল। দুপুরের আহারের পর নদীর নালন্দা হাওয়ায় বিশাল টানা বারান্দায় সবাই বসলে জমে উঠেছিল কোরাসে ইউসুফ- জুলেখার কাহিনী। সেদিন বাড়ীর সবাই মিলে ধামাইল নাচে উঠানে নেমে এসেছিলো। আমি ফ্রকের ঘের দুলিয়ে পা মেলাতে মেলাতে অবাক হয়ে বড় মানুষদের নাচ দেখছিলাম। দেখছিলাম নদীতে পাল টানিয়ে পাট নিয়ে চলে যাচ্ছে বিশাল গহনা নাও, ভেঁপু বাজিয়ে লঞ্চ আর স্টিমার, আরও দূরে ভৈরবের ব্রিজ দিয়ে সরীসৃপের মত ট্রেন। সেদিনের সে কিশোরীর মনের ক্যাম্পকর্ডারে তা এমন গাঢ় করে ধরা পড়েছিল যে আজ সত্তুর সন্নিকটে এলেও দেখছি তা সমান গতিতে প্লে হয়ে যাচ্ছে।
সে মহিলা জাঁদরেল হলেও কিন্তু ন্যায়বান ছিলেন।একবার মৌলভীবাজারের সম্পূর্ণ বয়স্ক সোনামামা তার শিশু পুত্রকে দুষ্টুমির জন্য চপেটাঘাত করাতে তিনি এত ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন যে তাৎক্ষণিক ভাবেই শীতল স্বরে মামাকে কাছে ডেকে প্রায় তার গালেই বসিয়ে দিচ্ছিলেন আরেকটি। আর তার নিজস্ব রুটিন হতে পারতো না একটুও নড়ন চড়ন। আমার ধারনা তাঁর ঐ পরিণত বয়সের সন্তানরা তাকে একটু ভয়ও করতেন। আমার ভয় লাগতো অন্য কারণে। পীর বংশের মেয়ে বলে, চন্দ্রচড়ির খ্যাতনামা ঈজহার আলীর কন্যা বলে, বাবার মত তিনিও মুখে মুখে চরণ বাঁধতেন বলে পীরানি মনে হত তাই। মনে হত তাঁর আধ্যাত্মিক একটা ব্যাপার আছে।
নানীভাই তার পুরানো সাদা শাড়িগুলো দিয়ে আমাকে ও খালাতো বোন রাজীকে পুতুল বানিয়ে দিতেন। আর পুতুলের সাদা মুখমণ্ডলে ঐ সুতো পাড় থেকে বের করা খয়েরী বা ঘন নীল সুতো দিয়ে ক্রিস ক্রস করে পেঁচ দিতেন। তাতেই আমাদের পুতুলের চোখমুখ ফুটে উঠতো। বৌ পুতুলের কাঠি হাতে সে সুতোতে হত চুড়ি। নারায়ণগঞ্জে চিলে কোঠায় জুতোর বাক্সে রেখে সেই পুতুল বর আর বৌ দিয়ে আমি আর রাজী খেলতাম। আমাদের কোলাহলে ছাদের রেলিঙে বসা পায়রা হঠাত উড়াল দিত।
আমার নানী ভাল দাবা খেলতেন। পড়ন্ত বিকেলে আমাদের দুরন্তপনাতে অস্থির হয়ে পড়লে স্থিত করতে ডেকে এনে খেলায় আটকে নিতেন। আটকাতে পারতেন না আমার ছোটভাই শুবুকে। কিন্তু আমি তিন চালের বেশি দাবাতে টিকে থাকার কোন ইতিহাস আমার নেই।
একটা সময় দেখা গেল তাঁর তিন পুত্রই বিলেতে জীবিকা ও জীবন নির্মাণ করে চলেছেন। এঁরা যখন লন্ডন আসা শুরু করলেন তখন এদের বিদায়ের দিন আগে থেকেই বাড়িতে জল ভরা বালতি বদনা সাজিয়ে রাখা হতো। আমরা ছোট ছোট পানসী নৌকারা -বাবলু ভাই , বুলু, ভাইয়া সেদিন মেজমামার বাসায় ঘোরাঘুরি করতাম। অপেক্ষায় থাকতাম মামা বেরিয়ে গেলেই নানীভাই উচ্চস্বরে ক্রন্দন করে কখন ফিট হবেন আর দৌড়ে গিয়ে বদনা ধরবো। এদিকে আবার যেদিন তাদের কেউ ফিরে আসতেন সেদিনও তাদের বুকে জড়িয়ে ধরে আবারো উচ্চস্বরে ক্রন্দন করতেন। এবারের আর ফিট হতেন না। এই আনন্দের কান্নাটার অর্থ বুঝতাম না এখন বুঝি। আমার ঈশিতা, সজীব বা আনাহিতাকে দীর্ঘ বিরতির পর দেখলে বুকে জড়িয়ে ধরার পর আমারও চোখ ভিজে আসে। এই করোনার ক্রান্তিকাল যখন শেষে হবে, তখন প্রথম যখন আনাহিতাকে দেখবো জানি তখন উচ্চস্বরে সই বলে তাকে বুকে জড়িয়ে আজকের এ নানীও আনন্দে কাঁদবে এবং শব্দ করেই। সে আমি নিশ্চিত।
শামীম আজাদ
 বৃটেনে সর্বাধিক জনপ্রিয় বাঙালি কবি হিসেবে পরিচিত । তিনি বাংলা ও ইংরেজী – দু’ ভাষাতেই লেখেন। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক – এর সবই তাঁর লেখনীর ক্ষেত্র। প্রকাশিত গ্রন্হ সংখ্যা ৩৭। তিনিই প্রথম বাংলাদেশী কবি ১৯৯৭ এ ভারতের স্বাধীনতার ৫০ বছর উপলক্ষ্যে আমেরিকার বিখ্যাত নিউইয়র্কার সাহিত্য সাময়িকীতে যাঁর কবিতার অনুবাদ ছাপা হয় এবং ২০১২ সালে বিশ্ব বিখ্যাত এডিনবরা ফ্রিঞ্জ ফেস্টিভ্যালে তিনি কবিতা ও গল্প পরিবেশন করেন। বিদেশে ও দেশে অন্যান্য নানাবিধ সম্মাননার সঙ্গে বাংলা একাডেমীর সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ পুরস্কারে ভূষিত।
বৃটেনে সর্বাধিক জনপ্রিয় বাঙালি কবি হিসেবে পরিচিত । তিনি বাংলা ও ইংরেজী – দু’ ভাষাতেই লেখেন। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক – এর সবই তাঁর লেখনীর ক্ষেত্র। প্রকাশিত গ্রন্হ সংখ্যা ৩৭। তিনিই প্রথম বাংলাদেশী কবি ১৯৯৭ এ ভারতের স্বাধীনতার ৫০ বছর উপলক্ষ্যে আমেরিকার বিখ্যাত নিউইয়র্কার সাহিত্য সাময়িকীতে যাঁর কবিতার অনুবাদ ছাপা হয় এবং ২০১২ সালে বিশ্ব বিখ্যাত এডিনবরা ফ্রিঞ্জ ফেস্টিভ্যালে তিনি কবিতা ও গল্প পরিবেশন করেন। বিদেশে ও দেশে অন্যান্য নানাবিধ সম্মাননার সঙ্গে বাংলা একাডেমীর সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ পুরস্কারে ভূষিত।
এই লেখাটি সর্বমোট 309 বার পঠিত হয়েছে । আজকে 1 জন লেখাটি পড়েছে ।