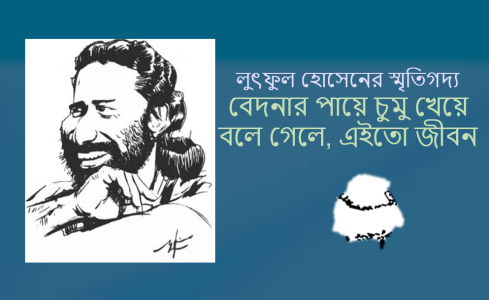[রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ (১৬ অক্টোবর ১৯৫৬-২১ জুন ১৯৯১) বাংলা কবিতার অন্যতম উজ্জ্বল কবি। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে লোকান্তরিত হন। কবিতার পাশাপাশি সংগীত, নাটক ও গদ্যচর্চাও করে গেছেন অবিরাম। তিনি ছিলেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট ও জাতীয় কবিতা পরিষদ গঠনের অন্যতম উদ্যোক্তা এবং জাতীয় কবিতা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম সম্পাদক। ১৯৭৫ সালের পরের সবকটি সরকারবিরোধী ও স্বৈরাচারবিরোধী সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিবাদী কবি হিসেবে খ্যাত। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, দেশাত্মবোধ, গণআন্দোলন, ধর্মনিরপেক্ষতা, ও অসাম্প্রদায়িকতা তার কবিতায় বলিষ্ঠভাবে উপস্থিত। তারুণ্য ও সংগ্রামের দীপ্ত প্রতীক কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ ৩৫ বছরের স্বল্পায়ু জীবনে সাতটি কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও গল্প, কাব্যনাট্য এবং “ভালো আছি ভালো থেকো”সহ অর্ধশতাধিক গান রচনা ও সুরারোপ করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে লেখিকা তসলিমা নাসরিন তার স্ত্রী ছিলেন। তবে বিয়ের ছয় বছর পর তাদের দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটে। ১৯৯১ সালের ২১ জুন রুদ্র মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ লোকান্তরিত হন। তিনি ১৯৮০ সালে পেয়েছেন মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার।
[রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ (১৬ অক্টোবর ১৯৫৬-২১ জুন ১৯৯১) বাংলা কবিতার অন্যতম উজ্জ্বল কবি। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে লোকান্তরিত হন। কবিতার পাশাপাশি সংগীত, নাটক ও গদ্যচর্চাও করে গেছেন অবিরাম। তিনি ছিলেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট ও জাতীয় কবিতা পরিষদ গঠনের অন্যতম উদ্যোক্তা এবং জাতীয় কবিতা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম সম্পাদক। ১৯৭৫ সালের পরের সবকটি সরকারবিরোধী ও স্বৈরাচারবিরোধী সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিবাদী কবি হিসেবে খ্যাত। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, দেশাত্মবোধ, গণআন্দোলন, ধর্মনিরপেক্ষতা, ও অসাম্প্রদায়িকতা তার কবিতায় বলিষ্ঠভাবে উপস্থিত। তারুণ্য ও সংগ্রামের দীপ্ত প্রতীক কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ ৩৫ বছরের স্বল্পায়ু জীবনে সাতটি কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও গল্প, কাব্যনাট্য এবং “ভালো আছি ভালো থেকো”সহ অর্ধশতাধিক গান রচনা ও সুরারোপ করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে লেখিকা তসলিমা নাসরিন তার স্ত্রী ছিলেন। তবে বিয়ের ছয় বছর পর তাদের দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটে। ১৯৯১ সালের ২১ জুন রুদ্র মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ লোকান্তরিত হন। তিনি ১৯৮০ সালে পেয়েছেন মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার।
১৬ অক্টোবর কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর জন্মদিন। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়ে এই লেখাটি নির্বাচন করা হয়। এই গদ্যের মূল উদ্দেশ্য কিছুটা ভিন্ন রুদ্রকে তুলে ধরা। বহুবার কচলে কচলে তেতো করে ফেলা গল্পগুলো থেকে বাইরে এসে, একজন প্রকৃত কবির একটি মৌলিক ও সাহসী জীবনকে স্মরণ করতে চেয়েছি আমরা। যেখানে অনেক না-জানা স্মৃতি সমাহার আছে, আছে একজন উদার উদাত্ত সৎ এবং সৃষ্টিশীল কবি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ]
বেদনার পায়ে চুমু খেয়ে বলে গেলে, এইতো জীবন
তকমার তল্পীবাহকরা যখন ব্যস্তসমস্ত তল্লাটের দখল নিতে। বনসাই চাইছে হয়ে উঠতে সৌন্দর্যের সংজ্ঞা। তখন কতজনই-বা সুরম্য-সুসজ্জিত অট্টালিকার বৈঠকখানা ফেলে বুনোফুল হয়ে উঠতে চায়! অমন পাগলামি তারই সাজে, যে খাঁটি, ভালোবাসে মাটি ও প্রকৃতি, যে নির্ভেজাল ও সত্যদর্শী। এ-কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পরিপূর্ণভাবে সত্যকে ধারণ করলেই স্তাবকতার বিপরীতে সোচ্চার হওয়া যায়, রাজ-রাজন্যের বিরুদ্ধে অকপট প্রতিবাদ জানানো যায়। আশির দশকে স্বৈরশাসকের আমলে যখন এই ঢাকা শহরে কবিরা বিক্রি হতে শুরু করেছিল পয়সার দামে, তখন সেইসব বিকিকিনির হাটে পণ্য না হয়ে বরং এর বিপরীত অবস্থানে দাঁড়িয়ে দর্শনীর বিনিময়ে কবিতা শোনাবার মতো পদক্ষেপ ও কর্মকাণ্ড ঘটাতে সৎসাহস লাগে, বুকের পাটা লাগে, মানুষ হওয়া লাগে। আর হ্যাঁ, বেড়ে ওঠায় বিশুদ্ধতা লাগে। একাকি দাঁড়াবার মতো চিন্তা চেতনা ও মনের জোর লাগে। নিগ্রহ-নিপীড়নের একই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে তাই সবাই নয়, অল্প ক’জনই দ্রোহী হয়, একজনই রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ হয়।
বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনের রেশ তখনও কাটেনি। ভাতভাপের পাক খাওয়া ধোঁয়ার মতো উত্তেজনা উপচে আসছে অস্থির সময়ের ফাঁক গলে। এমনই একটা সময়ে, ১৯৫৬ সালের ১৬ অক্টোবর বরিশাল রেডক্রস হাসপাতালে রুদ্রের জন্ম। তখন বাবার কর্মস্থল বরিশাল, সেইসূত্রে জন্ম বরিশালে জন্ম হলেও শিকড় তার বাগেরহাটের মোংলায়। দাদাবাড়ি সাহেবের মেঠ, নানাবাড়ি মিঠেখালি। দুটোই মোংলায় এবং খুব কাছাকাছি। নানাবাড়িতে বইয়ের অভাব নেই, রবীন্দ্র-নজরুল থেকে হালের লেখক-কবি, এমন কি ঢাকার ‘বেগম’ কিংবা কোলকাতার ‘শিশুভারতী’ পত্রিকাও নিয়মিত রাখা হয়। বইয়ের টানে মিঠেখালি ঘেঁষা রুদ্রের ক্লাস থ্রি পর্যন্ত স্কুল পর্ব চলেছে নানাবাড়ির পাঠশালায়। নানাবাড়ির আঙিনা ছেড়ে ’৬৬ সালে মোংলার সেন্ট পলস স্কুলে ভর্তি হন ক্লাস ফোরে। একাত্তরে ক্লাস নাইন, স্কুল আর হলো না। স্বাধীনতার পর রুদ্র ক্লাস টেনে ভর্তি হন ঢাকার ওয়েস্ট এণ্ড হাই স্কুলে। তিয়াত্তরে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে চার বিষয়ে লেটার মার্ক্স নিয়ে এসএসসি পাশ করলেও ঢাকা কলেজে ভর্তি হন মানবিক বিভাগে। ততদিনের সাহিত্যের নেশা তাকে পেয়ে বসেছে। ঢাকা কলেজে একঝাঁক সাহিত্যানুরাগী তরুণ সখ্যে কবিতার সঙ্গে রুদ্রের তুমুল বন্ধন প্রগাঢ় শিকড় হয়ে গড়ে ওঠে। পঁচাত্তরে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।
ডাক্তার বাবার দশ সন্তানের একজন। শৈশবে অন্তর্গত ইচ্ছে ছিল ডাক্তার হবেন। বাবার চেয়ে বড় ডাক্তার। বাবা-মায়েরও ইচ্ছে ছিল অমনই। অমনটা হলে নিশ্চিত তাঁরা অনেক খুশি হতেন। হোক বাবা তাকে কোনোদিন বুকে জড়িয়ে ধরেননি, কাছে ডাকেননি, খোঁজ-খবর রাখেননি। তবে শাসন ছিল কড়া। মাঠে খেলতে যাওয়া পছন্দ করতেন না। বলতেন ছেলেপুলে নষ্ট হবে অমন মাঠমুখো হলে। শৈশব-কৈশোরের দিনগুলোতে এর চেয়ে বেশি বেদনার কী হতে পারে? ভিতরে যত বেদনা থাকুক, রাগ-ক্ষোভ থাকুক; মাঠমুখো তার আর হওয়া হয়নি। ডাক্তার হওয়াটাও না। সময়টা তখন উত্তাল আর বয়সটা সবে চৌদ্দ। ঠিক যে বয়সে কৈশোরের উত্তুঙ্গ আবেগ-উত্তেজনায় উদ্বেল হয়ে ওঠে একটা ছেলে। তারুণ্যের কাছাকাছি, উদাস অভিমান তাড়িত এমন বয়সে তার দেশে শুরু হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ। পড়াশোনা বন্ধ, বন্ধ স্বাভাবিক জীবনের যাবতীয় আচার। সমস্ত বোধ-অনুভূতি গ্রাস করে নিয়েছে যুদ্ধের নির্মমতা, ভয়াবহতা, অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা। অন্তহীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উত্তাপ উত্তেজনা রক্তের ভিতর তার বপন করে যায় বিপ্লব ও দ্রোহের বীজ।
সেই বায়ান্ন থেকে তুষে চাপা আগুন জমা হতে হতে, জমা হতে হতে, দাবানল হবার জন্যে লাগাম ছিঁড়তে মরিয়া। দেশের আপামর মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়লো মুক্তিযুদ্ধে। পূর্বাপর বিবেচনা ছাড়া, খালি হাতে যারা যুদ্ধে গেল, আবেগ আর ভালোবাসাই ছিল তাদের প্রধান অস্ত্র। কিন্তু এই যুদ্ধটা এলোমেলো করে দিয়ে গেল অনেক মানুষকে অনেক রকম ভাবে। স্বজন হারাবার শোক ছোঁয়নি এমন পরিবারের দেখা পাওয়া ভার। কিন্তু সবচেয়ে বেশি এলোমেলো হলো আবেগতাড়িত তারুণ্য।
ডাক্তারি পড়ার ইচ্ছায় ভাটা পড়লো তার। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে এসে নিলেন বাংলা বিভাগে স্নাতকে পড়ার সিদ্ধান্ত। কবিতা লেখার নেশায় ডুবতে শুরু হওয়াটাই সম্ভবত এমন সিদ্ধান্তের সবচেয়ে বড় প্রভাবক। কবিতা, কবি, আড্ডা; জীবনকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবার একটা অভিযাত্রা। জন্মাবধি দেশজুড়ে নিজ ভাষা, অধিকার আর নায্য হিস্যার জন্য চলমান যে অস্থির উন্মাদনা তাকে গ্রাস করেছিল ভিতরে ভিতরে। লেখায় সেইসব দ্রোহ, ভালোবাসা অমন অপূর্ব সাচ্ছন্দ্যে তুলে আনার নজির কমই আছে। তীব্র খেদ, তুঙ্গ ক্ষোভ, গভীর ভালোবাসা পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে কবিতার শরীরে তার বুনেছে অভিন্ন নকশা। অকপট উচ্চারণে তার রোমান্টিক বিপ্লবী ও দ্রোহের কলম তাই অনায়াসে লিখেছে ‘ভুল মানুষের কাছে নতজানু নই’।
এরকম কথার অগণিত উচ্চারণ আছে তার অসংখ্য কবিতায়। বলতে গেলে সমস্ত লেখায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। সবচেয়ে বেশি তাড়িত করেছে আমাকে তার গ্রন্থ শিরোনামগুলো। ১৯৭৯-১৯৮২ এই চার বছরে প্রকাশিত তার দুটি কাব্যগ্রন্থের নামগুলোর কথাই যদি ভাবি! ‘উপদ্রুত উপকূলে’ (১৯৭৯), ‘ফিরে চাই স্বর্ণগ্রাম’ (১৯৮১)। উপদ্রুত উপকূল তো গোটা দেশটাই। স্বাধীন হয়েও সোনার দেশটাকে খুঁজে ফিরেছে দেশপ্রেমিক সকল মানুষ। খুঁজে ফিরেনি কি! ভিতরের কবিতাগুলোর কথাও যদি ধরি! প্রথম কাব্যগ্রন্থের একটা উদাহরণ তো সকল কবিতাপ্রেমীরই মুখস্ত। ‘বাতাসে লাশের গন্ধ’। দ্বিতীয় বইয়ের পর, ১৯৮৪তে বেরুলো ‘মানুষের মানচিত্র’। যাপিত জীবনের প্রতিকৃতিই তো এইসব নাম!
রাজনৈতিক বোধে সজাগ সচেতন রুদ্র দলীয় রাজনৈতিক চর্চায় সম্পৃক্ত না থাকলেও ১৯৭৮ সালের ডাকসু নির্বাচনে কেন্দ্রীয় পরিষদের সাহিত্য সম্পাদক প্রার্থী ছিলেন ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে। ১৯৭৯ সালে বিভাগীয় প্রধান ডক্টর আহমদ শরীফ ক্লাসে উপস্থিতি হার কম থাকায় পরীক্ষা দিতে অনুমতি না দিলে রুদ্র স্নাতক পাশ করেন ১৯৮০ সালে। ইতোমধ্যে তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছে। নানাবিধ সাহিত্য সাংস্কৃতিক সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার কারণে স্নাতকের পর স্নাতকোত্তরেও দুবছর তার পরীক্ষা দেয়া হয়ে ওঠেনি। ১৯৮১’র বদলে রুদ্র বাংলায় স্নাতকোত্তর পাশ করেন ১৯৮৩ সালে। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শুরু থেকে বেহিসেবি সময় দিয়েছেন শিল্প-সাহিত্য অনুরাগ ঘিরে নিজস্ব অঙ্গীকারে। সময় দিয়েছেন প্রেমে। মিটফোর্ড হাসপাতালে নবীন ডাক্তার স্ত্রীর সঙ্গে লালবাগমুখি হবার আগে বারবার মারিয়েছেন ঢাকা-ময়মনসিংহের পথ। ১৯৮১ সালের ২৯ জানুয়ারি বিয়ে করেছেন।
‘রুদ্রকে আমি আমার সতেরো বছর বয়স থেকে চিনি। সেই সতেরো বছর বয়স থেকে রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ আমার সমস্ত চেতনা জুড়ে ছিল। আমাকে যে মানুষ অল্প অল্প করে জীবন চিনিয়েছে, জগৎ চিনিয়েছে- সে রুদ্র। আমাকে যে মানুষ একটি একটি অক্ষর জড়ো করে কবিতা শিখিয়েছে- সে রুদ্র।’ এমন গভীরতা থেকে শুরু হয়েও প্রমত্ত পদ্মা-যমুনা থেমে যায় ১৯৮৬ সালে। পাঁচ বছরের এই দাম্পত্য ছাড়াও ভালোবাসা ছুঁয়েছে রুদ্রের হৃদ-আঙ্গিনা অন্তত একাধিকবার। কিন্তু কখনোই পরিণতির দিকে তা কিছুমাত্র এগোয়নি। দেশ মাটি মানুষকে ভালোবেসে সাম্যের আকাঙ্ক্ষা বুকে ধারণ করে, দ্রোহ ও প্রতিবাদের উচ্চারণে সকল সময় উচ্চকিত থাকার পাশাপাশি ভালোবাসার বিরহবেদনা নিরন্তর ছোবলে তাকে ক্ষতবিক্ষত করে গেছে নিয়তই।
দ্রোহ প্রেম ভালোবাসার ক্যানভাস জীবনের বিস্তারে ছড়াতে থাকলে তাই স্বভাবতই ক্রমাগত পালটায় বীক্ষণ। তারই সূত্র ধরে গড়ে উঠেছে তার কাব্যনির্মাণ ছাঁচ, গ্রন্থের শিরোনাম। ১৯৮৬ তে প্রকাশিত তার চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ ‘ছোবল’ এমন সত্যই উন্মোচন করে। ১৯৮৭ তে ‘গল্প’ গ্রন্থ-শিরোনামটিও তো আর কিছুই না। জীবনটা যে বাস্তবতার প্রহসনে কেবলই একটা গল্প হয়ে উঠেছে। সে কথাই বলেছে প্রকারান্তরে। ইতিমধ্যে ব্যক্তিগত টানাপোড়েন দখল করেছে তার অগণিত দিন-রাত্রির উদ্যান। ফের আকাশটাকে মুঠোয় পুরেও কেবলি ফস্কে যাবার জীবনই তো গড়ে দেয় ১৯৮৮’র গ্রন্থ শিরোনাম, ‘দিয়েছিলে সকল আকাশ’। হয়তো কোথাও দ্রোহ, প্রতিবাদ, প্রেম, ভালোবাসার আড়ালে জমেছিলো খেদ, অনুচ্চার আহাজারি, আক্ষেপ। আর শেষে এসে সম্ভবত আপন আবিষ্কারকেই উচ্চারণ করেছেন ফের তাঁর গ্রন্থ শিরোনামে। ‘মৌলিক মুখোশ’ (১৯৯০)। চারিদিকে মুখোশের ছড়াছড়িই তো। নয় কি! জীবনের পরও তাই প্রকাশ পায় তার ‘বিষ বিরিক্ষের বীজ’ (কাব্যনাট্য)। এসবের বাইরে রুদ্র দিয়ে গেছে অর্ধশতাধিক গানের কথা ও সুর। রুদ্র তার প্রথম দুটি বইয়ের জন্যেই রুদ্র ১৯৮০ ও ১৯৮১ সালে সংস্কৃতি সংসদ প্রবর্তিত মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেছিল। তা বাদে আর কোনো পুরষ্কার পাওয়া না পাওয়া তার হয়তো বিবেচ্য ছিল না। কিন্তু পাঠকের হৃদয়ে রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ যে বেঁচে থাকবেন বহুকাল তা ক্রমশ প্রগাঢ় সত্য হয়ে উন্মোচিত হচ্ছে তার অকাল প্রস্থানের পর থেকেই।
ভিতরে যতই ঝড়-ঝঞ্ঝা চলুক রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ মানে যাপনের প্রতিটি ক্ষণ উচ্চকিত প্রাণখোলা হাসি। রুদ্র মানেই বন্ধুবাজি। রুদ্র মানেই আড্ডার কেন্দ্রস্থল। রুদ্র মানেই হাজারো রকম মানুষের অতি প্রিয়জন, প্রিয় বন্ধু। ঢাকা ছেড়ে মোংলায় চলে গেলে মেঘে ঢাকা পড়তো টিএসসি, হাকিম চত্ত্বর, বাংলা একাডেমি, বই মেলা, শাহবাগ, সাকুমনি, হাটখোলা; হয়তো সমস্ত ঢাকা। অকস্মাৎ কোনোদিন মেঘ সরে গিয়ে সূর্য উঁকি দেয়া মানেই রুদ্রের ফিরে আসা। ঢাকার আড্ডা জোয়ারের ঢেউয়ের মতোন অবিরাম তীরে আছড়ে পড়া। চারপাশের প্রতিটা প্রিয় মানুষের প্রতি তার ছিলো একটা আলাদা রকমের সাম্পর্কিক যত্ন। বিশেষ করে তরুণ লিখিয়েদের প্রতি রুদ্রের আচরণ ছিল অন্য সবার চাইতে ভিন্ন। নিজ উদ্যোগে তরুণ লিখিয়েদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, তরুণ লিখিয়ের বই কেনা, এইসব আচরণে তার মতো উদারহৃদয় মানুষের দেখা কদাচই মেলে। আজও আড্ডায় রুদ্র প্রসঙ্গে যদি কেউ কিছু বলে তো একটা কথা নিশ্চিত উচ্চারিত হয় এবং হবে, ‘অমন ভালোমানুষ খব কমই হয়, অমন উদার মনের মানুষ খুব কমই হয়’।
তার অনুপস্থিতির আঁধার ছাপিয়ে ঢাকা উচ্ছল হয়ে উঠলে ভাবতাম মিঠেখালি-মোংলায় নিশ্চয় এখন মেঘ জমছে। কিন্তু সেই ভাবনার দৌড় বেশিদূর যেতে পারতো না। রুদ্রের উপস্থিতি মানেই যে ঝকঝকে রোদ্দুর। এ শহরের পানশালা প্রাণ পেতো রুদ্রকে পেলে। মিছিল বেসামাল উদ্দাম হতো রুদ্রের উচ্চারণে। মঞ্চ-শ্রোতা উচ্ছল হতো তার কবিতার উচ্চারণে। আঁধার পঁচাত্তর থেকে নব্বুইয়ের গণ আন্দোলনে রুদ্র শুধু কবিতায় নয়, মিছিলে শ্লোগানে, দ্রোহের উচ্চারণে সক্রিয় থেকেছে সকল সময়। বাম রাজনীতির চিন্তা-চেতনা তারুণ্যে তাকে রাজনীতি শিখিয়েছিলো অনেকের মতো। তবে সেটার প্রয়োগ রুদ্র করে গেছে একবেমাদ্বিতীয়মের মতো। কবিতাও রাজনীতির মূলধারায় ভূমিকা রেখেছিলো যে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে, তার উজ্জ্বল নক্ষত্র নির্দেশকদের সেরা একজন রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ। রুদ্র অমনই একজন সৌভাগ্যবান কবি, যার সকণ্ঠ কবিতা পাঠ শুনতেই শুধু নয়, যাকে দেখতে দেশের আনাচ-কানাচ থেকে লোক আসতো ঢাকায়, তার সন্ধানে।
১৯৮৭তে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবেই জন্ম হয় জাতীয় কবিতা পরিষদের। রুদ্র ছিলেন জাতীয় কবিতা পরিষদের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম-সম্পাদক। স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের নিমিত্তে গড়ে ওঠা সংগঠনটির প্রথম জাতীয় কবিতা উৎসব শিরোনাম ছিল ‘শৃঙ্খল মুক্তির জন্য কবিতা’। প্রথম এই আয়োজনের উৎসব সংগীতটি ছিল রুদ্রেরই লেখা। একই সময়ে গড়ে ওঠা সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের প্রথম আহ্বায়ক কমিটির সদস্য এবং বাংলাদেশ সংগীত পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও প্রকাশনা সচিব রুদ্র। ‘অন্তর বাজাও’ নামে একটি গানের দল গড়েছিল রুদ্র। ওই গানের দল নিয়ে দেশের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছে। চলচ্চিত্র নির্মাণের পরিকল্পনাও করেছিল। ৩৪ বছরের ক্ষণজন্মা জীবন যদিও তাকে শেষ অব্দি সেই সুযোগ দেয়নি। তবে রাখাল এবং দ্রাবিড় নামে আরো দুটো সংগঠনের সাথেও তার জোর সম্পৃক্ততা ছিল।
এমনই উত্তাল সময়ে জাতীয় কবিতা পরিষদকে ঘিরে দূরের দেখা রুদ্র হয়ে উঠলো কাছের মানুষ। বড়দের আড্ডায় বেশিরভাগ সময় কাটানো আমার জন্যে টিএসসিতে রুদ্র ও তার বন্ধুদের সাথে আড্ডাটা ছিলো নেশার মতোন। মাঝে মাঝে হাকিম চত্ত্বরে, বেশিরভাগ দিন টিএসসিতে আড্ডা শুরু হয়ে এগুতো শাহবাগে। সেখান থেকে সাকুমনি। তারপরও কোনোদিন গড়াতো হাটখোলায়। স্বৈরাচারের অবরুদ্ধ সময়ও থামাতে পারেনি সে সময়ের তারুণ্যকে। এমন বিপ্লবী তারুণ্য, বিবিধ সংগঠন, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট এবং জাতীয় কবিতা পরিষদ ঘিরে রুদ্রের ছিল নানান ভাবনা ও পরিকল্পনা। কবিতা উৎসবকে কেন্দ্র করে কিংবা অমন নানা অনুষ্ঠান ঘিরে সারা দেশ থেকে ঢাকায় আসা কবিদের থাকা-খাওয়ার সমস্যাকে কেন্দ্র করে, তার ইচ্ছে ছিল সরকারের কাছে আবেদন করে জাতীয় কবিতা পরিষদের নামে একটা পরিত্যক্ত সম্পত্তির বাড়ি বরাদ্দ নেয়ার। যেখানে পরিষদের দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড চালাবার পাশাপাশি সাশ্রয়ী দামে ঢাকায় আগত কবি-সাহিত্যিকদের থাকা-খাওয়ার একটা ব্যবস্থা থাকবে। শুধু এটাই নয়, এমন নানান উদ্ভাবনী ভাবনা-চিন্তা শুধু নয় সাংগঠনিক নানা কাজে বোহেমিয়ান রুদ্র ছিল ঠিক বিপরীত এক চরিত্র। জাতীয় কবিতা পরিষদের নানা মিটিঙে অমন রুদ্রের চাক্ষুস সাক্ষী আমার মতন অনেকে, বিশেষত তরুণেরা, রুদ্রের সকল প্রস্তাব-প্রস্তাবনা বা যুক্তি-তর্কের নিরবচ্ছিন্ন সমর্থক ছিলাম। কারণ কবিতা-গান, লেখালেখি কিংবা এইসব সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কোনো সংগঠন ঘিরে রুদ্রের কাজকর্ম ছিল গোছানো, পরিপাটি। কোনো একটা লেখাকে বারে বারে সম্পাদনা করে মনমতো দাঁড় করানো কিংবা এইসব সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের নথিপত্র সংরক্ষণ এসবে রুদ্র এমনই গোছানো ছিল যেনো সবচেয়ে গোছানো মনযোগী মানুষটিকেও অনায়াসে হার মানাবে। বাইরে থেকে বাউণ্ডুলে রুদ্র, জীবনকে মুঠোয় পুরে তিন তাসের টেবিলে ছুঁড়ে ফেলা রুদ্রকে যারা চেনে তাঁদের অধিকাংশই হয়তো ভেতরের এই রুদ্রের হদিস কখনও জানেনি।
কবিতার নানা অনুষ্ঠানে দেশের যে কোনো প্রান্তে যাবার অনিয়মিত রুটিন ছাড়া রুদ্র রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ মাঝে মধ্যে লম্বা সময়ের জন্য চলে যেতেন তার মিঠেখালি মোংলার ঘেরে। কয়েকটা রিকসা ছিল রুদ্রের। সেইগুলোয় আয় ছাড়াও নানারকম ঠিকাদারি কাজ করতো। এরকম একবার, রুদ্র ঢাকায় নেই বেশ কিছুদিন। মিঠখালি গেছে তার চিংড়ির ঘেরে। ওখানে ছৈয়ের মধ্যে দিন-রাত কাটিয়ে দেয় সে টানা। বাড়িঘরও ওখানে পাশেই। যে নানাবাড়িতে কেটেছে তার শৈশবের সর্বাধিক সময়, সেখানটার খুব কাছেই ঘের। নানাবাড়ির স্কুলে যখন পড়া শুরু হয়, সেই আমল থেকে ওখানেও গড়ে উঠেছিল তার বিবিধ বন্ধুত্ব। যদিও বাবার সঙ্গে একটা দূরত্ব তাকে বাড়িবিমুখ করে রাখতো অধিকাংশ সময়। তবু মায়ের সঙ্গে ছিল তার গভীর যোগাযোগ। মোংলা থেকে ফিরলে নিশ্চয়ই তার কোথাও না কোথাও টান খেতো অন্তর্গত সুতায়। কিন্তু দেখে বুঝবার উপায় খুব একটা ছিলো না কখনোই।
এরকম এক বিকেলে মুহসিন হল থেকে হেঁটে যাচ্ছি টিএসসির দিকে। হাকিম ভাইয়ের চায়ের দোকানটা পার হয়ে কয়েক কদম আসতেই দেখা গেল এইদিকে মুখ করে একটা বেঞ্চিতে রুদ্র বসে আছে। তখন টিএসসির বৃত্তাকার দেয়ালের বাইরে সামনে বেঞ্চি পেতে চায়ের দোকান ছিল কয়েকটা। একদম মাঝ বরাবর ছোটো একটা অংশ দেয়ালবিহীন। তার দুপাশে দুটা দোকান ছিলো সবচেয়ে জমজমাট। এখনকার মতো এতো ভীড় ছিল না। গাঢ় বাদামি রঙের একটা ট্রাউজার। প্রায় ড্রেস-শু টাইপ একজোড়া স্নিকার্স। গায়ে প্যান্টের চাইতে এক-দুই শেড হালকা বাদামী একটা হাতা গুটানো ফুলশার্ট, বোতামওয়ালা দুটা বুকপকেট, কাঁধে স্ট্র্যাপ। হাতে প্যাঁচানো মোটা ব্রেসলেট। কাছাকাছি হতেই ইশারায় ডাকলো। সামনে আসতেই খোঁজ নিলো, কেমন আছি, কেমন ছিলাম। অন্য আরো যারা আমার মতোন হলে থাকা একই আড্ডার মানুষ, তাদের কথা জানতে চাইলো। একসময় বললো এবার গানটায় মনমতো সুর দিয়ে ফেলেছি।
সেবার মেলায় একদিন সবাই রুদ্রকে ঠাট্টা করছিলো, ক্ষ্যাপাচ্ছিল। কেউ একজন বললো নামটা বলেন। হা হা করে হেসে বলে উঠলো রুদ্র, আরে নামটাই তো জানা হয়নি। কিছুক্ষণ পর দেখা গেলো বিড়বিড় করে বলছে, আমি তার নাম জানি না, দেখলে চিনি। দেখতে দেখতে এভাবেই কোনো কোনো দিন আড্ডায় তৈরি হয়ে যেতো একটা আস্ত কবিতা কিংবা কবিতার ভিত। তেমনি একদিন আউড়ে যাচ্ছিলেন, ভালো আছি ভালো থেকো, আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো। আজ ওটার কথাই বললো, আরও লাইন একসাথে জুড়ে গোছানো হয়ে গেছে ওই গানটা। সুরও মনের মতো দাঁড়িয়ে গেছে। একটু পরই একে একে আড্ডায় মানুষ বাড়তে থাকলো। আমার আর শোনা হলো না পুরোটা। শোনা হলো না সুরটা। আমি তাই আড্ডা ছেড়ে উঠছি না। সেই আড্ডা টিএসসি থেকে শাহবাগ হয়ে সাকুরায় যখন পৌঁছুলো তখন আমাদের নির্ধারিত টেবিলে অন্য কারা যেনো বসে পড়েছে। কাউন্টার আমাদের থামিয়ে বললো, একটু দাঁড়ান টেবিল খালি করে দিচ্ছি। রুদ্র মানা করলেও তারা পাত্তা দিলো না। আর এমন আড্ডা রুদ্রের পকেটে টাকা থাকা পর্যন্ত থাকতো চলমান। তো আড্ডা যখন থামলো মাঝরাতের কিছুটা আগে। তখন রুদ্রের স্ফীত পকেট শীর্ণ।
সবাইকে একে একে বিদায় করে এবার সে চললো হাটখোলা। আমার একটু কেমন কেমন লাগছিলো। কিন্তু এক মুড়িওয়ালাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে মুরগির ঝোল সমেত মাখিয়ে যে মুড়িটা সেদিন খেয়েছিলাম সেটাই সম্ভবত আমার খাওয়া সবচেয়ে সেরা মুড়িমাখা। রাত যখন মধ্যবর্তী সীমানা পেরিয়ে এক ঘন্টা এগিয়েছে, তারও পর আমরা বেরুলাম। আজ সে আর আমার মুহসিন হলের রুমে যাবে না। বললো রাজাবাজার যাবে। বাসায়। আমি একটু আড়ষ্ট হয়ে পড়লাম। এর আগে আমি যাইইনি। আজ এমন সময়ে। আশ্বস্ত করে বললো, মা নেই, বড়রা কেউ নেই, শুধু ছোটো বোন আছে। একটা স্কুটার নিয়ে আমরা রওনা দিলাম হাটখোলা থেকে রাজাবাজারের দিকে। সেই তুমুল ভটভট শব্দ তোলা ওই স্কুটারের মধ্যে পাল্লা দেয়া রুদ্র উচ্চস্বরে গান ধরলো, ‘ভালো আছি ভালো থেকো, আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো’। আমি নিঃশব্দে মুগ্ধ হয়ে শুনছি। স্কুটার ভটভট করে এগিয়ে যাচ্ছে। রমনার পাশ দিয়ে শেরাটন পার হয়ে সেই সাকুরাকে বাঁয়ে ফেলে ফার্মগেটের দিকে।
রাজাবাজারে আমরা যখন পৌঁছুলাম তখন রাত দুটা। ছোট্ট দোতলা বাসার বারান্দায় বোন জিজ্ঞেস করলো, দাদা টেবিলে ভাত দেবো? রুদ্র আমার দিকে তাকাতে মানা করলাম। সন্ধ্যা থেকে পালায় পালায় মুড়ি-চানাচুর, চিকেন ফ্রাই, মুরগি ভূনা আর শেষে ফের মুড়িমাখা। সোনালি শিশির তো ঝরছিলোই। পেটে আর জায়গা কোথায়! শুধু পানির তেষ্টা ছিলো। আর দুচোখ ছাপিয়ে ক্লান্তি। অপেক্ষায় দরোজায় দাঁড়ানো ঘুম।
তখনও কি জানতাম! আকাশের ঠিকানায় বাড়িবদল হবে তার আতো তাড়াতাড়ি! দেখতে দেখতে স্বৈরাচারের পতন ঘটলো। শহরে নতুন বাতি লাগলো। মঞ্চে মঞ্চে কবিতা পড়ার জন্য মাইকের দিকে ভীড় করবার লোক বাড়তে থাকলো। দর্শনীর বিনিময়ে কবিতা পড়ার মতো উদ্দীপ্ত, হৃদয় কাঁপিয়ে দেয়া কবিদের আমরা খুঁজতে শুরু করলাম, খুঁজতে থাকলাম। জীবন গোছাতে ব্যস্ত আমার সঙ্গে শেষদিকে রুদ্রের দেখাসাক্ষাৎ কমে গেলো অনেক। আর আমি টেরই পেলাম না আড্ডার অমন প্রাণপুরুষকে এক জীবনের জন্য হারাতে যাচ্ছি এভাবে অকস্মাৎ! আজ যতবার রুদ্রের গান শুনি বাজছে কোথাও। যতবার কাউকে দেখি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর কবিতা পড়ছে, সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করছে, তার ভিতর থেকে হয়তো উঠে আসে স্মৃতির পুরোনো অর্কিড। আমার ইচ্ছে হয় না বইয়ের পাতা উলটে দেখি কোনটার নীচে লেখা মিঠেখালি মোংলা, কোনটায় পশ্চিম রাজাবাজার, কোনটায় ৪০২ মুহসিন হল। ইচ্ছে হয়না আবার পড়ে দেখি ‘মিছিলে নতুন মুখ’ কবিতার লাইনে সে আমাকে নিয়ে কি লিখেছিল। ওসব করতে গেলেই প্রচণ্ড শ্বাসকষ্টে ভোগা এক রোগীর মতো আমার বুক ভেঙে আসতে থাকে ব্যথায়। ব্যথা কি তবু আমার কিছুটা ভালো লাগে! ওইখানে রুদ্রের স্মৃতি থেকে থেকে পত্রপল্লব মেলে!
১৬ অক্টোবর ২০২০
রুদ্র মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ প্রকাশিত গ্রন্থ:
কবিতা: উপদ্রুত উপকূল (১৯৭৯);ফিরে চাই স্বর্ণগ্রাম (১৯৮১); মানুষের মানচিত্র (১৯৮৬); ছোবল (১৯৮৬);গল্প (১৯৮৭); দিয়েছিলে সকল আকাশ (১৯৮৮); মৌলিক মুখোশ (১৯৯০)
ছোটগল্প: সোনালি শিশির
নাট্যকাব্য: বিষ বিরিক্ষের বীজ
বড়োগল্প: মনুষ্য জীবন
লুৎফুল হোসেন

কবি, প্রকাশক ও সাহিত্যকর্মী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর। বিভিন্ন রকমের পোর্টাল ও পত্রিকায় নিয়মিত গল্প, কবিতা, ফিচার, প্রবন্ধ এবং গান লিখছেন। বাংলাদেশের লিটলম্যাগ ও নানা প্রকাশনা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত আছেন সেই ছাত্র থাকাকালীন সময় থেকেই। শৈল্পিক মননশীলতাকে প্রশ্রয় দিয়ে একটু একটু করে গড়ে তুলছেন তার নিজস্ব প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ‘রচয়িতা’।
এই লেখাটি সর্বমোট 557 বার পঠিত হয়েছে । আজকে 1 জন লেখাটি পড়েছে ।