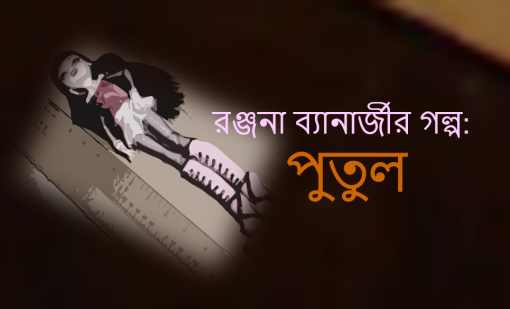রাবি ফুফুর শেষ ইচ্ছে অনুযায়ী পুতুলটি তাঁর কফিনেই দেওয়া হয়েছে। তাঁর প্রাণহীন দেহের পাশে অপটু হাতে তৈরি কাপড়ের পুতুলটি বড় বেশি জীবন্ত লাগছিল। রাবি ফুফুর মেয়ে লিজি, ফুফুর অসাড় বাহুর নিচে সুকৌশলে গুঁজে দিয়েছিল যেন কাচের ঢাকনা ফুঁড়ে ওর উপস্থিতি অকারণ কৌতূহলের কারণ না-হয়। কিন্তু কফিনের কাছে যেতেই পুতুলটার মুখ আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। লাল সুতোতে সেলাই করা আবছা হাসির দিকেই চোখ আটকে গেল। স্পষ্ট শুনলাম রাবি ফুফুর গলা: সকল ঘটনাই স্বতঃস্ফূর্ততায় একটি নির্দিষ্ট সমাপ্তির দিকে গড়িয়ে যায়…আমার পেছনে বেশ লম্বা লাইন। আত্মীয়-স্বজন ছাড়াও রাবি ফুফুর বন্ধু এবং সহকর্মীদের অনেকেই শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এসেছেন। আমি দ্রুত সরে আসি।
এই ফিউনারেল-হোমের আলোক-সজ্জায় কেমন একটা জন্ডিসের ভাব। জানালার রঙিন কাচের চিত্রকল্পে বাইবেলের গল্প; তাতেও হলুদের বাড়াবাড়ি। বাইরের মরা রোদ আর ভেতরের হলুদ এই দুইয়ের মিশেলে কাচে আঁকা তিন জ্ঞানীর মুখে অদ্ভুত বিষণ্ণতা মাখিয়ে দিয়েছে। তাঁরা যেন আগাম জেনে গেছেন ঈশ্বরের পুত্র অচিরেই ক্রুশবিদ্ধ হবেন! খড়ের বিছানায় শোয়া শিশু-যিশুকে দেখা না গেলেও ভেতরে ওর দেহের ভার বেশ বোঝা যাচ্ছে।
প্রার্থনার সুর সিলিঙ ছুঁয়ে বিষণ্ণতার ছাতা মেলে দিচ্ছে। অদ্ভুত সব ভাবনা বুদবুদ তুলছে আমার মনে। ঘটনাগুলোর একটার সঙ্গে অন্যটার কোনো সংযোগ নেই। এক অমোঘ নিয়তির টানে এরা যেন একে অপরকে অনুসরণ করেছিল।
সব কিছু অবিশ্বাস্য দ্রুততায় ঘটেছিল। ঠিক চৌত্রিশ দিন আগে ফুফু নিজেই ফোন করে সেই ভয়ঙ্কর সংবাদটি দিয়েছিলেন। এর আগে তেমন কোনো শারীরিক সমস্যা ছিল না ফুফুর। হঠাৎ অফিসে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষে জানা গেলো রিনাল সেল কার্সিনোমা। স্টেইজ ফোর। মেটাস্টেটিক। প্রতিটি শব্দ বরফের শেলের মতো আমাদের মগজে বিঁধছিল। ফোনের এপাশে আমি আর মার্ক ধাক্কা সামলে যখন কী বলব হাতড়াচ্ছি, তিনিই মীমাংসা দিলেন, ‘সান্ত্বনা বা ভরসা কোনটিই আমাকে ভালো বোধ করাবে না। শরীর বশে থাকতে থাকতে যতটা পারি গুছিয়ে নিতে চাই। জনকে তো চেনো। সংসারে থেকেও বৈরাগী। কাল এক কার্টন পুরনো ছবি বার করেছি। মার্কের অনেক ছবি আছে। এইসবের প্রিন্ট শ্যন-মার্থার(আমার শ্বশুর-শাশুড়ি)কাছে নেই। কাল এসে বেছে নিয়ে যেও।’
জানলাম লিজি ফিরে এসেছে। লিজি অন্য প্রদেশে আন্ডার-গ্র্যাড করছে। পরদিন কাজ শেষে লালীকে ডে-কেয়ার থেকে তুলে ফুফুর বাড়ি পৌঁছাতে বেশ দেরি হয়ে গেল। লালীকে পেয়ে ফুফু আগের মতোই মেতে উঠলেন। লিজির সঙ্গে চোখ মেলাচ্ছিলাম না। একটু টোকা লাগলেই লিজি ভেঙে পড়বে। মার্ক এই সব ভালো সামলাতে পারে। ওর আসতে আসতে সন্ধ্যা গড়িয়ে যাবে। আমি সহজ হওয়ার ছুতো খুঁজছিলাম। বললাম, ‘খুব খিদে লেগেছে ফুফু’! আগের দিনের মিট-পাইয়ের বেশ খানিকটা রয়ে গেছে ফ্রিজে। সেটা বার করতে গেলেন ফুফু। আমিই ঠেকালাম। বেবি ক্যারিয়ার খুলে লালীর অ্যাপেল-সস ধরিয়ে দিয়ে বললাম, ‘তুমি বরং নাতনীর সেবা কর। আমি নিজেই নিচ্ছি।’ ফুফু হেসে লালীকে নিয়ে লিভিং রুমে সরে গেলেন। ফুফু যেতেই লিজি আমায় জড়িয়ে ধরল। হাহাকার করে বলল, ‘কেন এমন হলো তিতির!’ ওর চোখের জলে আমার কাঁধ ভিজে যাচ্ছিল। তখনও জানতাম না কী এক অদ্ভুত ঘটনার অংশী হতে যাচ্ছি আমি!
খাওয়া-দাওয়ার পরে বেইসমেন্টে রাজ্যের ছবি নিয়ে বসেছিলাম আমরা। ছবির পেছনের গল্পগুলো শুনতে শুনতে মনের মেঘ খানিক ফিকে হয়েছিল। লালী খুব বিরক্ত করছিল। ওকে ব্যস্ত রাখতে ফুফু লিজির ছেলেবেলার স্টাফড-টয়ের প্যাঁটরাটা বের করলেন। অ্যালবাম ছেড়ে লিজি লালীকে নিয়ে ব্যস্ত হলো। হঠাৎ লিজির উচ্ছ্বাস, ‘মাম্মি এটা এখনও আছে!’ আমি কৌতূহলে মাথা ঘোরাতেই চমকে উঠলাম! আমার গা হাত পা কাঁপছিল। চোখে ভাসছিল সেই শীর্ণকায় মহিলার মুখ। ‘যত্ন কইরে রাইখো। বৈদেশ গেলে নিয়ে যাইও’। সেটিরও এমন কাঠি কাঠি হাত-পা। চোখ-নাক-মুখও সেলাই করেই ফোটানো। ন্যাড়া মাথা। নিশ্চিত হতে হাত বাড়িয়ে পুতুলটা নিয়েছিলাম। ‘কোথায় পেয়েছ এটা?’ নিজের কাছেই নিজের গলা অচেনা ঠেকছিল। ফুফু নয় লিজিই উত্তর দিয়েছিল, ‘মাম্মির সঙ্গে সেই আশ্রম থেকেই দেওয়া হয়েছিল। মাম্মির আসল মায়ের হাতে তৈরি।’ মনে হচ্ছিল আমার পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে। হে ভগবান! এত কাছাকাছি থেকেও আমি জানলাম না! আমার সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। ‘তোমাদের ট্র্যাডিশন্যাল কিছু?’ ফুফু আমার হতভম্ব অবস্থা দেখে জানতে চাইলেন। আমি সামলে নিয়ে বললাম, ‘বলতে পারো। আমাদের দেশের বালিকারা এক সময় এমন পুতুল বানিয়ে খেলতো।’ এরপরে হাল্কা করে জানতে চাইলাম, ‘এই পুতুল যিনি বানালেন তাঁকে তোমার দেখবার ইচ্ছে হয় নি?’ ফুফু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, ‘নাহ্, আমার সাত বছরের জন্মদিনের পরদিনই মাম্মি-ড্যাডি জানিয়েছিল দত্তক নেওয়ার ব্যাপারটা। এই পুতুলটাও মাম্মি দিয়েছিল সেইদিন। বলেছিল যত্ন করে রাখতে এটা আমার আসল মায়ের উপহার। আমার তখন অনেক বার্বি। এটি ওদের তুলনায় ম্যাড়ম্যাড়ে তাই বিশেষ কিছুই মনে হয় নি। দত্তক মানে কী সেটাও তো স্পষ্ট বুঝিনি। পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে ভয়ানক গোলমেলে ছিল। ড্যাডি বলেছিলেন, ‘ঈশ্বর মাঝে মাঝে ভুল জায়গায় পাঠিয়ে দেন শিশুদের, পরে আবার আসল বাবা-মায়ের কাছে ফিরিয়েও দেন। আমরাই তোমার আসল বাবা- মা’। এই কথাটাই আমি এখনও সত্য মানি। তাই হয়তোবা কখনই পেছনের কথা জানতে ইচ্ছে হয় নি। পুতুলটা পরে মাম্মিই রেখেছিল। বিয়ের পরে দিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, ‘আসল মায়ের আশিস’, ফুফু হাত বাড়িয়ে পুতুলটা নিয়ে নিলেন। বুঝলাম এই প্রসঙ্গে আলাপ এখানেই শেষ।
পুতুল বাদে দত্তকের কাহিনীটা আমার আরও আগেই জানা। মার্কের সঙ্গে আমার পরিচয় ইউনিভার্সিটির কফিশপে। আমি বাংলাদেশী, এই তথ্যই ওকে কৌতূহলী করেছিল। সম্পর্ক গাঢ় হলেই জেনেছিলাম ওর কৌতূহলের পেছনের কথা। মার্কের পিতামহ- পিতামহী দুজনেই চিকিৎসক ছিলেন। এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্য হয়ে বাহাত্তরের মাঝামাঝি বাংলাদেশে গিয়েছিলেন। মূলত তালুকাটা এবং হাড়ের বৈকল্যে আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসা-সেবা দেওয়াই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। উত্তরবঙ্গের সেই মিশনারি আশ্রমে বাচ্চাটার বাঁ-পায়ের গোড়ালির হাড়ে সমস্যা ছিল। বয়স তিনমাস। স্বাস্থ্য-পরীক্ষার সময় পিতামহী ডেভির আঙুল শক্ত করে ধরে রেখেছিল বাচ্চাটা। কটা চোখ, এক মাথা চুল যেন দেবশিশু। ডা. ডেভির ভেতরে অদ্ভুত এক অনুভূতি হয়েছিল। ওদের একমাত্র পুত্র যিনি পরবর্তীতে আমার শ্বশুর হবেন তিনি তখন গ্রেড সেভেনে পড়েন, বোর্ডিং স্কুলে। আরেকটা বাচ্চা নেওয়ার কোনো পরিকল্পনাই ছিল না। দুজনেই ব্যস্ত। দেশে তো বটেই অনুন্নত বিশ্বের যে কোনো জায়গায় তালু-কাটা শিশু এবং হাড়ের রোগীদের চিকিৎসা সেবা দেওয়ার সুযোগ ছাড়তেন না তাঁরা। কিন্তু ডা. ডেভি সেইদিন শিশুটির আঙুল ধরাকে ঈশ্বরের নির্দেশ হিসেবে দেখেছিলেন। স্বামীকে দত্তক নেওয়ার ইচ্ছে জানাতেই তিনিও রাজি হয়ে গিয়েছিলেন।
ডা. ডেভিকে আমি দেখি নি। আমার বিয়ের আগেই তিনি স্বর্গবাসী হয়েছিলেন। তবে গ্র্যান্ড-পি পিটার আমার বিয়ের পরেও পাঁচ বছর বেঁচে ছিলেন। বিয়ের পরপরই আন্ট রাবি নয় রাবি ফুফু সম্বোধনের সিদ্ধান্ত নিই আমি। বলেছিলাম ‘বাংলাদেশে আমরা বাবার বোনকে ফুফু কিংবা পিসি বলি, তোমায় আমি রাবি ফুফু ডাকবো।’ ফুফু নিজেও তাঁর নামে ‘বসরি’ অংশটুকু না থাকলেও জানতেন সেই সুফি-সাধ্বীর কথা। তাই আমার প্রস্তাব সানন্দে মেনে নিয়েছিলেন। সেই দিন গ্র্যান্ড-পি পিটারও উপস্থিত ছিলেন। পুতুলের গল্পটা কথা প্রসঙ্গে উঠতেই পারত। কেন উঠল না তা আজও আমার কাছে রহস্য।
রাবি ফুফুর বাড়ি থেকে বেশ রাত হয়েছিল ফিরতে। ট্রেনে লোক নেই বললেই চলে। সেই সুযোগেই সেইদিন পুতুল দেখার ঘটনাটার উল্লেখ করে অনুযোগ করেছিলাম, ‘দশ বছর হয়ে গেল তোমাদের পরিবারে অথচ আজই দেখলাম রাবি ফুফুর আসল মায়ের দেওয়া সেই পুতুলটা।’ মার্ক ততোধিক অবাক হয়ে বলল, ‘এটা কি বিশেষ কিছু?’ বললাম ‘চেষ্টা করলেই আমি এই পুতুল দিয়েই রাবি ফুফুর আসল মায়ের খোঁজ বার করতে পারি।’ মার্কের চোখে বিহ্বলতা। ‘কেন? যতদূর জানি আন্ট রাবির এই ব্যাপারে কোনো আগ্রহই ছিল না। এখন এসব বলছে? মাই গুডনেস ভাগ্যিস গ্র্যান্ড পি আর গ্র্যান্ড মা নেই। কী কষ্টই না পেতো তাঁরা!’ আমি বললাম, ‘কী কষ্ট পেতো ভেবেই হয়তো রাবি ফুফু তাঁর নিজের ইচ্ছে দমিয়ে রেখেছিলেন। এটা আমার প্রস্তাব। রাবি ফুফু কিছু বলেন নি’। একমুহূর্তের জন্য মার্ক যেন স্তম্ভিত হলো এর পরেই গলায় রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে বলেছিল, ‘তোমার ব্যক্তিগত কৌতূহল অন্যের গোপনীয়তা ভঙ্গ অথবা কষ্টের কারণ হতে পারে সেটা মাথায় রাখা উচিত, আমাদের সংস্কৃতিতে এটাই দস্তুর।’ মনে হয়েছিল যেন কেউ আমাকে সপাটে চড় লাগাল। চরম অপমান নিয়ে সারারাস্তা আমি আর মার্কের সঙ্গে কথা বলিনি।
এর পরেও প্রায় কুড়ি দিন আমি নিজের সঙ্গে শলা করেছি, দায়বদ্ধতা এবং উচিত-অনুচিতের নিগুঢ় সম্পর্ক বোঝার চেষ্টা করেছি। ইতোমধ্যেই বাড়িতেও ফোন দিয়েছিলাম। এবং জেনেছিলাম আমাকে দেওয়া পুতুলটা বাড়ির জঞ্জাল কমানোর যজ্ঞে হাপিশ হয়েছে। যে পুতুল আমাদের সেই আঁটসাঁট ফ্ল্যাটে ওঠার সময়ও হাতছাড়া করেন নি মা তা কীভাবে এমন গুরুত্বহীন হলো! বুঝতে অসুবিধা হলো না যে মায়ের সংসারের কর্তৃত্বের চাবিটিও চিরতরে হারিয়ে গেছে।
শেষ দশ-বারো দিন ফুফুর শরীর দ্রুত খারাপের দিকেই গড়াচ্ছিল। তারপরেও তিনি হাসপাতালের প্যালিয়েটিভ কেয়ারে যেতে রাজি হচ্ছিলেন না। নার্স আসতেন বাড়িতে। এক বিকেলে আমরা সবাই লিভিং রুমে বসেছি। ফুফু নার্সের তত্ত্বাবধানে ভেতরঘরে। টিভিতে কিছু একটা চলছিল সেইদিকে তাকিয়ে আমরা যে যার ভাবনায় ডুবে ছিলাম। ফুফু এলেন। আমাদের এই পিনপতন নীরবতা দেখে তাঁর স্বভাবসুলভ টিপ্পনী কাটলেন, ‘বাব্বা এ তো দেখি রীতিমত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মহড়া চলছে। খবরদার আমার সার্ভিসে এমন দুঃখ দুঃখ ভাব করে থাকবে না’। ফুফু্র কথা শেষ না হতেই লিজি কান্না শুরু করে দিয়েছিল। রাবি ফুফু হুইলচেয়ার ঠেলে সটান লিজির পাশে গেলেন। ফুফুর কোলে মাথা রেখে লিজি ফুলে ফুলে কাঁদছিল। আমরা কেউ লিজিকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষাও খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ফুফু বললেন, ‘লিজি আঁধারে তারা না দেখলে হাল ছেড়ে দেওয়া তো ঠিক না বরং আঁধারে পথ চিনে চলতে শেখো। এই কষ্ট চিরকালীন নয়’ এরপরেই ফুফু সেই অদ্ভুত কথাটা বললেন, ‘মনে রেখো সকল ঘটনাই স্বতঃস্ফূর্ততায় একটা নির্দিষ্ট সমাপ্তির দিকে গড়িয়ে যায়।’ আমার ভেতরে কিছু একটা ঘটল! মনের সব দ্বিধা উবে গেল। স্থির করলাম সেই পুতুলের কারিগরের কথাটা ফুফুকে বলবই। কিন্তু পরদিন সকালেই ফুফুর প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়াতে জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো।
বিকেলে হাসপাতালে গিয়ে জানলাম রাবি ফুফুর অক্সিজেন লেভেল খানিক বাড়লেও বিপদসীমার নিচে নয়। ডাক্তার কোনো আশ্বাস দেন নি বরং শেষ বিদায়ের জন্য প্রস্তুতি নিতে বলেছেন। রাবি ফুফুর কাছে একজনের বেশি যেতে দিচ্ছিল না। আংকেল জনকে আমি ফুফুর সংগে কিছুক্ষণ থাকতে চাই বলতেই তিনি নার্সকে বলে আমায় ভেতরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। নার্স জানাল রোগী কড়া ব্যথানাশকের ঘোরে আছেন। দশ মিনিটের জন্য আমায় একা থাকতে দিয়ে নার্স বেরিয়ে গেল। কীভাবে শুরু করব বুঝতে পারছিলাম না। আমি ফিসফিস করে ডাকলাম । ফুফু চোখ খুললেন না। আমি তাঁর হাতের ওপর আলতো করে হাত রাখলাম। ফুফুর হাত কাঁপল খানিক। আমি বললাম, ‘ফুফু আমি তিতির’, ফুফুর হাত কাঁপল আবার। বুঝলাম ফুফু শুনছেন। ভণিতা না করেই বললাম, ‘ফুফু তোমার মাকে আমি ছেলেবেলায় দেখেছিলাম। তিনি তখন তোমার খোঁজে পুতুল বানিয়ে বিলিয়ে বেড়াতেন।’ ফুফুর হাত স্থির হয়ে রইল। আমি সেই ঘটনা বলা শুরু করলাম। যা লিখছি এখন তার পুরোটা বলিনি তাঁকে। যতটা কমে সত্য বলা যায় ততটাই বলেছিলাম। কিন্তু ঘটনাটার পুরোটাই যেন আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল আমি সেই সময়টাই যাপন করছি।
আমি তখন ফোরে পড়তাম। বাবার বদলির সুত্রে আমরা সেই জেলা শহরে দুই বছর ছিলাম। তিনতলা বিল্ডিংয়ের নিচতলায় আমরা থাকতাম। বারান্দায় একটা বেতের দোলনা ছিল আর ছিল মায়ের নানা জাতের বেলি-ডালিয়ার ঝাড়। মুখোমুখি দুটো বিল্ডিং-এর মাঝখানে ছিলো পার্কিং লটটা। মা-বাবা পারতপক্ষে বাইরের বারান্দায় বসতো না। বারান্দাটা আমার দখলেই থাকতো ছুটির দিনে। কখনো রান্নাবাটি কখনো বা মেঝেতে উবু হয়ে আইসক্রিমের কাপে রাখা জলের ভেতরে তুলি ডুবিয়ে ছবি আঁকতাম। স্পষ্ট মনে আছে সেই দিন আমি ছবিই আঁকছিলাম। আমার ড্রইং খাতা চুপসে গিয়েছিল ভেজা তুলির টানে। হঠাৎ হইচই। উপর তলার আন্টি চেঁচাচ্ছিলেন। মা, দাদা ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। বাবা ছিল না বাড়িতে। খানিক পরেই দরজায় টোকা পড়েছিল। আন্টি তখনও রেলিংয়ের উপর ঝুঁকে গালাগাল দিচ্ছিলেন। মা দরজা খুলতেই আমিও দেখলাম মহিলাকে। মলিন পোশাক। পাখির মতো কাঁপছেন। আমাদের দরজা খোলার আওয়াজে আন্টিও দুদ্দাড় করে নেমে এলেন। মহিলার চোখেমুখে আতঙ্ক। কাঁধের ঝোলাটি বুকের কাছে ঢালের মতো চেপে ধরে ছিলেন। মা মহিলাকে কী চাই জিজ্ঞেস করতেই উনি ঝরঝর করে কেঁদে দিয়েছিলেন। এরপর জানিয়েছিলেন উনি একটা পুতুল দিতে এসেছিলেন। মা অবাক হয়ে জানতে চাইলেন, ‘কাকে?’ অনেক কসরতের পর মহিলার কথা উদ্ধার হয়েছিল। তিনি শুনেছিলেন এখানে লন্ডনী বেগমসাহেবা থাকেন। দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করলে দারোয়ানও এই বাড়িটিই দেখিয়ে দিয়েছিল। আর এই লন্ডনী শুনেই আন্টি খেপেছিলেন। আন্টির বাপের বাড়ির সকলে লন্ডন থাকেন। সম্প্রতি টেন্ডার নিয়ে অনিয়মের তদন্তে আংকেলের নাম উঠে এসেছে। লন্ডন-সংযোগ সেই গুজবে হাওয়া দিচ্ছিল। কিন্তু এই লন্ডনীকে পুতুল দেওয়ার বিষয়টা কী? তখনই সেই অদ্ভুত ঘটনা শুনিয়েছিলেন মহিলা। আমার চোখে এখনও ভাসছে তাঁর সেই ন্যাড়া মাথার পুতুলে ঠাঁসা মলিন ঝোলা। নয় বছরের আমি সেই মুহূর্তে এই কাহিনীর গভীরতা বুঝিনি। যাওয়ার সময়ে তিনি আমাকেই সেই ঝোলা থেকে একটা পুতুল বার করে দিয়ে বলেছিলেন, ‘যত্ন কইরে রাইখো। বৈদেশ গেলে নিও’। কথাটা বলার সময় তাঁর চোখের কোণে অদ্ভুত এক হাসি চমকেছিল। মনে রাখার মতো কোনো বিশেষ মুখ ছিল না কিন্তু সেই হাসির আভাসটি এত বছর পরেও স্মৃতিতে জেগে আছে।
সেই গল্পের পেছনের বেদনা অনুভব করেছিলাম আরো পরে। তখন আমি এইচ. এস. সি. দেবার প্রস্তুতি নিচ্ছি। বাবা রিটায়ার করেছেন। দাদা বিয়ে করেছেন। মেহেদিবাগে আমাদের ১২০০ বর্গফুটের সদ্য কেনা ফ্ল্যাটে ওঠার আগে বাড়ির কী যাবে, আর কী বিক্রি হবে এবং কী কী ফেলে দেওয়া হবে তার গোছগাছের যজ্ঞ চলছিল। আমার পরীক্ষার পরেই পাকাপাকি উঠে যাব এই নতুন স্থায়ী ঠিকানায়। পুতুলটা আমার ছেলেবেলার নানা স্মারক বোঝাই একটা বাক্সে তোলা ছিলো। ওটা খালি করতে গিয়েই বেরিয়ে এলো। আমাদের নতুন বৌদিকে এই পুতুলের কাহিনী আবার শোনালেন মা। আট বছরের ব্যবধানে গল্পটা একটুও পাল্টায় নি। তবুও আনকোরা হয়েই আমার কাছে ধরা দিয়েছিল: একাত্তরে তের বছর বয়সের কিশোরী ছিলেন মহিলা। পাকিস্তানী সৈন্যরা তুলে নিয়ে গিয়েছিল। দেশ স্বাধীন হলে অন্যদের সঙ্গে তাঁকেও উদ্ধার করা হয়। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত কিশোরী তার নির্যাতনের মাত্রা মাপে নি। যুদ্ধকালীন শারীরিক নির্যাতন যে স্বাধীন দেশে মানসিক নিপীড়নে পাল্টাবে তার আন্দাজ করার বয়সে পৌঁছায়নি সে। পাড়ার লোকেরা ভিড় করে দেখতে আসত যেন তিনি চিড়িয়াখানার কোনো জীব। যৌতুকের টোপেও পাত্র জোটে নি। অতঃপর তাকে ‘খালাস’ করাতে শহরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এক দূর-সম্পর্কের মামার বাসায় উঠেছিলেন। কিশোরীর মনে প্রকৃতির নিয়মেই হয়তোবা মাতৃত্ববোধ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সেই দুঃস্বপ্নের দিনগুলি সরে নতুন এক আলোর রেণু ছড়িয়েছিল মনে। মাঝে মাঝে ব্যথায় মন ভরে যেত। বাড়িতে নতুন বাচ্চা মানেই ছোটো ছোটো কাঁথা, জামা। রোদ মাখানো আঁচারের বৈয়াম। অথচ তাঁকে ঘিরে কেবল বাপ-মায়ের দীর্ঘশ্বাস এবং স্বজনদের ফিসফাস। এক দুপুরে কী মনে হতেই তিনি নিজেই নিজের সাদা ওড়না কেটে একটা পুতুল বানালেন। মামানি জানতে চাইল, কার জন্য পুতুল? বললেন, মেয়ের জন্যে। মামানি অবাক হয়ে বললেন, ‘তুমারে কে কইসে মাইয়া অইব?’ কিশোরীর ধারণা ছিল সব মা-ই জানে তাদের ছেলে হবে নাকি মেয়ে হবে। যেদিন পুতুলের ঠোঁটে লাল সুতো দিয়ে হাসিটি ফোটালেন সেদিনই তার ব্যথা উঠল। বাচ্চাটিকে তিনি দেখেন নি। ‘ও আল্লাহ সত্যই মাইয়া!’ মামানির সেই আবছা আওয়াজ কানে নিয়ে তিনি জ্ঞান হারিয়েছিলেন। চোখ খুললে তাকে জানানো হয়েছিল বাচ্চার ভালোর জন্যই মিশনারি আশ্রমে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তবে তার বানানো পুতুলটাও বাচ্চাকে দেওয়া হয়েছে। তার কান্নায় আকাশ জমিতে নেমে এলেও বাচ্চা ফেরেনি।
বাড়ি ফিরিয়ে আনার দুইমাস পরে পাত্র পাওয়া গিয়েছিল। তিন বাচ্চার বাপ। তিন নম্বরকে বিইয়েই বৌ শয্যা নিয়েছে। মূলত এই তিন নম্বরের দেখভালের জন্যেই দ্বিতীয় বিবাহ। তাও দক্ষিণের ধানী জমি যৌতুক দিতে হলো। মেয়ে যে আর্মিক্যাম্পে ছিল তা জানা আছে পাত্রের। সবাই ভেবেছিল এবার হয়তো মন ঘুরবে মেয়ের। কিন্তু এই বিয়ে তাঁকে ফের ফিরিয়ে দিলো সেই হায়েনাদের স্মৃতি। দিনের বেলায় শিশুর দেখভাল সতীনের চোখা কথা আর রাতে স্বামীত্বের নামে বর্বরতা। তারপরেও ফাঁক পেলেই কান ভরে থাকত সেই অদেখা কন্যার কান্নার আওয়াজে। এক দুপুরে বাচ্চাটিকে ঘুম পাড়িয়ে সাত পাঁচ না-ভেবেই পালালেন। শহরের সেই দূরসম্পর্কের মামা-বাড়ি পৌঁছে গিয়েছিলেন বিকেলের আগেই। ভাগ্যিস মামা ছিল না বাড়িতে। মামানী তাঁর কান্নাকাটি দেখে সেই আশ্রমের ঠিকানাটা দিয়েছিলেন। তার আগে অবশ্য আল্লার কিরে খাইয়ে নিয়েছিলেন যেন কেউ না-জানে এসব।
আশ্রমের গেটের ভেতর ঢুকতে দেয় নি তাঁকে। সন্ধ্যা থেকে রাত গাঢ় হলেও তিনি মাটিতেই জেদ ধরে বসে রইলেন । দারোয়ানের ধমক ধামকে কাজ না হলে অবশেষে তাঁকে ভেতরে ঢোকানো হয়। পরির মতো ধবধবে সাদা বিদেশী সিস্টার তার সবকথা শোনেন। এরপরে জানান বাচ্চা বিদেশে ওর নতুন মা-বাবার কাছে এবং অনেক যত্নে আছে। বাচ্চাকে দেখানো আপাতত সম্ভব নয়। তাঁর কান্না ইট সিমেন্ট ভেদ করে রাস্তায় গড়িয়ে পথচারীদেরও চকিত করছিল হয়তোবা কারণ সিস্টার তড়িঘড়ি জানিয়েছিলেন যে চিঠি লিখে দত্তক মা-বাবাকে তার সব কথা জানাবেন। ওরা বাচ্চাকে অবশ্যই তাঁকে দেখাতে নিয়ে আসবেন। কিশোরী চোখ মুছে জানতে চেয়েছিল একটা পুতুল বানিয়েছিল বাচ্চার জন্যে সেটা কি বাচ্চাকে দেওয়া হয়েছে? ওর মেয়ের একটা নামও ঠিক করেছিল সে মনে মনে। সিস্টার ওর মাথায় হাত বুলিয়ে জানিয়েছিলেন, পুতুল দেওয়া গেছে। নামটাও নিশ্চয় রাখা হবে। বাচ্চা কোন দেশে জিজ্ঞেস করলে বলেছিলেন বিদেশে। এরপর সিস্টার ওকে পাউরুটির উপরে লাল জেলি মাখিয়ে খেতে দিয়েছিলেন। দারোয়ানকে দিয়ে বাসেও তুলে দিয়েছিলেন।
তিনি বাপের বাড়িই ফিরে গিয়েছিলেন। রাতে চোখ বুজলেই মনে হতো শরীরের উপর কেউ চড়ে বসেছে। আর চোখ খুললে মনে হতো কোথাও কাঁদছে বাচ্চাটা। সকাল হলেই উৎকর্ণ থাকতেন কেউ এলো কি তাঁর খোঁজে? এক রাতে মনে পড়ল সিস্টার তো ঠিকানা জানতে চায় নি! অমনি সব এলোমেলো হয়ে গেলো আবার। ভোর না হতেই গঞ্জের বাস ধরে শহরে চলে এসেছিলেন। কিন্তু আশ্রমের গেইটের সামনে এসে দেখেন বিল্ডিংয়ের রঙ পালটে গেছে। এটি এখন এক ওষুধ কোম্পানির স্থানীয় অফিস। ‘সিস্টার লেনের আশ্রম’ নামের সেই খ্রিষ্টীয় উপাসনালয় এবং আশ্রয়কেন্দ্রটি আট দশ মাস আগেই উঠে গেছে! কোথায়? কে খোঁজ রাখে! সেই বুড়ো দারোয়ানের চেহারা ছবির বর্ণনা শুনেও কেউ হদিশ দিলো না। তিনি রাস্তার উপর বসেই বুক ভেঙে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর অসংলগ্ন কথার কোনো খেই পেলো না কেউ।
বাড়ি ফিরে আসতেই হলো। যাওয়ার জায়গা নেই আর। কাঁদতে কাঁদতে একসময় কান্নাও ভুলে গেলেন। ক্রমশ তিনিও সকলের নজর এড়িয়ে দাদী-আম্মার ঘরের এককোণে নিজের ছায়ার ভেতরেই গুটিয়ে থাকতেন। এক দুপুরে দাদী-আম্মার কাঁথার নক্সার জন্য শাড়ির পাড়ের সুতো তুলতে গিয়েই পুতুলের কথা মনে পড়ল। পরির মতো সিস্টার ঈশ্বরের ক্রুশ গলায় ঝুলিয়ে নিশ্চয় মিথ্যা বলবেন না। তাঁর দেওয়া নামটা না রাখুক পুতুলটা নিশ্চয় তাঁর মেয়ের কাছে পৌঁছেছে। তখনই এই অভিনব চিন্তা তাঁর মাথায় আসে। সেই পুতুলের মতো পুতুল যদি তিনি ‘বৈদেশে’ পাঠাতে পারেন তবে মেয়ে তাঁর খোঁজ পাবেই। সেই থেকে তাঁর পুতুল বানানো শুরু এবং সুযোগ পেলেই সেই পুতুল নিয়ে তিনি শহরে আসেন। খুঁজে বেড়ান বৈদেশের সংযোগ। রাবি ফুফুকে এই ঘটনা বলতে গিয়ে দুটো নতুন তথ্য আমার সামনে এলো যা আগে খেয়াল করিনি। যে সময়ে মহিলা আশ্রমে গিয়েছিলেন সেই সময়ে শিশু রাবি ওখানেই ছিলেন। দত্তকের ঘটনা ঘটে পরে। সেই সিস্টার কথা রেখেছিলেন। রাবেয়া নাম এবং পুতুলটিও মেয়ের সঙ্গে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়টি হলো লন্ডন সংযোগ। এই লন্ডন শব্দটি আমার নিজের মাথায় কোনো কারণে গেড়ে বসেছিল বলেই হয়তোবা ফুফুকে বাহাত্তর সনে দত্তক নিয়েছে শুনেও ‘যুদ্ধশিশু’ কিংবা ‘পুতুল’– এই বিষয়গুলো মগজে টোকা দেয় নি। আর লন্ডনী খুঁজতে এসেছিলেন বলেই লন্ডনের সঙ্গেই শিশুটিকে জুড়ে দিয়েছিলাম আমরা নিজেরা। মহিলা লন্ডন নয় ‘বৈদেশ’ বলেছিলেন বরাবর।
আমার কথা ফুরিয়ে গেলেও আমি এইসব ছাইপাঁশ ভাবছিলাম। কখন নার্স ঢুকেছে খেয়ালই করিনি। ফুফুর দিকে তাকিয়ে দেখি তাঁর চোখ বোজা। এতক্ষণ যা বললাম তা শুনলেন কি? ফুফুর হাত ছাড়তে গিয়ে মনে হলো ফুফুর আঙুল নড়ছে। নার্সকে বলতেই নার্স ফুফুর মুখের কাছে কান নিয়ে জানতে চান কিছু বলবেন কিনা। ফুফুর চোখের পাতা কাঁপছিল। একফোঁটা জল গড়িয়ে নামল গাল বেয়ে। নার্স বলেন ‘লভ’ বলছেন। আমার চোখের জলের বাঁধও ভেঙে গেল এই কথা শুনে। আমি ফুফুর হাতে চুমু খেয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম।
ফোনটা এলো রাতে। লিজির গলায় উচ্ছ্বাস, তড়বড়িয়ে বলল, ‘মা তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে বলেছে। কেন তিতির?’ আমি চুপ রইলাম। লিজি ঘাঁটাল না। বলল, ‘মাকে কী ভালো দেখাচ্ছে! তুমি কাল আসবে তো? তিতির মিরাক্যাল হতেও পারে তাই না?’ আমি কী বলব বুঝতে পারছিলাম না।
পরদিন ফুফুই আমাকে ডেকেছিলেন। আমি গেলে হাত বাড়ালেন। আমি হাত ছুঁয়ে বললাম, ‘ফুফু আমাকে মাফ করে দাও। সেই দুপুরে পুতুল দেখেও আমি বলতে পারিনি দ্বিধার কারণে’। ফুফু মুখে হাসি টেনে ফিসফিস করে বললেন, ‘আমার মা কেমন দেখতে?’ আমি বললাম, ‘পরির মতো’। ফুফুর কথা বলতে গেলেই কাশি উঠছিল। কাশতে কাশতেই নিজের দিকে আঙুল দেখালেন। আমি আন্দাজেই উত্তর দিলাম, ‘তোমার চেয়েও সুন্দর’। তিনি মৃদু হাসলেন। আমি বলতে পারলাম না ফুফু হয়তো সেই পশুটার চেহারারই ছাপ পেয়েছে। তবে এর পরে তিনি যা বললেন তার জন্যে আমি তৈরি ছিলাম না। কেবল তিনটি শব্দ। ‘লিজি, জন, নো’। আমি নিশ্চিত হতে বললাম, ‘ওদের বলব না?’ উনি ঠোঁট টিপে বললেন, ‘সিক্রেট’ এরপর আঙুল তুলে নিজেকে দেখালেন এবং আমাকে। তারপরেই বললেন, ‘পুতুল কফিনে’। আমি কাঁদতে থাকলাম। এবার উনি পুরো একটি বাক্য বললেন সময় নিয়ে ধীরে, ‘এর পরে যদি কিছু থাকে তবে পুতুল দেখেই মা চিনে নেবে। আমি বললাম, ‘উনি বেঁচে নেই কে বলল?’ ফুফু দম নিলেন। একটা একটা শব্দ যেন বুকের গহীন থেকে উঠে আসছিল, ‘নেই। থাকলে তোমার–আমার দেখা হতো না’। তারপরে বুকে আঙুল রেখে বললেন, ‘পিস’। আমি ফুফুর বুকে আলতো করে মাথা রাখলাম।
আরও দুই দিন বেঁচেছিলেন ফুফু।
রঞ্জনা ব্যানার্জী

জন্ম চট্টগ্রামের এক সম্ভ্রান্ত শিল্পানুরাগী পরিবারে। পড়াশোনা বেড়ে ওঠা চট্টগ্রামেই। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়ন শাস্ত্রে মাস্টার্স করেছেন। দীর্ঘদিন শিক্ষা ক্যাডারে চাকুরিরত ছিলেন। ২০০৪ সনে স্বামীর কর্মসূত্রে নর্থ আমেরিকায় পাড়ি জমান। দুই সন্তানের জননী রঞ্জনা ব্যানার্জী বর্তমানে কানাডার প্রিন্স এডওয়ার্ড আইল্যান্ডের রাজধানী শার্লটাউনের বাসিন্দা এবং একটি বায়ো- ট্যাকনোলজি ফার্মে কর্মরত।
প্রকাশিত বই :
আহেলি-(গল্প সঙ্কলন, প্রকাশক: শৈলী প্রকাশন, ২০১৭)
একে শূন্য-(গল্পসংকলন প্রকাশক: বাতিঘর, ২০১৯)
তেত্তিরিশ-(অণুগল্প প্রকাশক: বাতিঘর, ২০২০)
এই লেখাটি সর্বমোট 378 বার পঠিত হয়েছে । আজকে 1 জন লেখাটি পড়েছে ।