এই তো আর ক’দিন পরেই পহেলা বৈশাখ এসে যাবে আমাদের দোরগোড়ায়। জানি, বাংলাদেশ এখন অবরুদ্ধ কোভিডের কারনে। অন্যবারের মতো বালাদেশের আনাচ-কানাচ রং আর রেখায় ভরে যাবে না।হয়তো রং উঠে আসবে না মেয়েদের শাড়ীতে, ছেলেদের পাঞ্জাবীতে, নানান ফুলের সমাহারে, তোরনের বর্নচ্ছটায়। রেখা তার স্হান করে নেবে না আলপনায়, দেয়ালে, প্রতিচিত্রে।
আর্ট কলেজের ছেলে-মেয়েরা সারারাত জেগে ঢাকার রাস্তায় আলপনা আঁকবে না, দেয়াল চিত্র শেষ করবে না, নানান রংয়ের আর ঢংয়ের মুখোশ বানাবে না, রঙীন কাগজের প্রতিমূর্তি গড়বে না পরদিন প্রভাতের শোভাযাত্রার জন্য। উন্মাদনা, উৎসাহের জোয়ার দেখা যাবে না চারদিকে – আনন্দ, স্ফূর্তি আর উৎসবের আমেজ অনুভব করা যাবে না আকাশে-বাতাসে।
এবার হয়তো বরন করে নেয়া যাবে না নতুন বছরকে প্রীতি-সম্ভাষনে, গানে, আমোদে আর মুখরোচক খাদ্যে। মেলা বসবে না নানান জায়গায়, রমনার বটমূলে বসবে না গানের আসর, চিরায়ত বাঙ্গালী খাবার উঠে আসবে না আমাদের রসনায়।নারী-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো, শিশুদের কলকাকলিতে ঘন হয়ে আসবে না আকাশ-বাতাস।
জানি না, এই সব চালচিত্র পেরিয়ে মন কখন যেন চলে গেছে অনেক দূরে – প্রায় ৬০ বছর আগে। ছবির মতো বরিশাল শহরের বেশীর ভাগই ছিল লাল সুরকির। ব্রজমোহন কলেজ সংলগ্ন আমাদের দোতালা কাঠের বাড়ীর ধার ঘেঁষে যে পথটি চলে গেছে, তা শহর পেরিয়ে কাশীপুর হয়ে চলে গেছে। ঐ পথ ধরেই বাস যেত রহমতপুর, ভূরঘাটা, গৌরনদী, চাখার আরো কত জায়গায়।যতবার বাস যেত, ততবারই একটি লাল ধূলোর ঘূর্ণি উঠত রাস্তার ওপরে ক্ষনিকের জন্য। তারপর তা মিলিয়ে যেত।
কিন্তু একদিন সেই লাল ধূলোর ঘূর্ণি ঘন হয়ে বসে যেত বাতাসে। এবং সেটা ঐ পহেলা বৈশাখেই। সারা বরিশাল শহরে ঐ পথ ধরে রওনা হত পশ্চিমে বেলা ৩টায় শুরু হওয়া কাশীপুরের বৈশাখী মেলার দিকে।রিক্সায়, সাইকেলে, পদব্রজে লোকের যাত্রা শুরু হয়ে যেত সেই দুপুর ১২ টা থেকেই।সে জনস্রোতের একটা বিরাট অংশই ছিল শিশুরা – ঐ যে মেলার মাটির পুতুলের জন্য।গরুর খুরের সৃষ্ট ধূলি থেকে ‘গোধূলি’ শব্দটি এসেছে, কিন্তু আমাদের বরিশালে পহেলা বৈশাখে মানুষের হেঁটে চলার পায়ে পায়ে যে মনুষ্যধূলির সৃষ্টি হত, তার কাছে গোধূলি তো নস্যি।
বেশ মনে আছে, ছোটবেলায় বড় কারো হাত ধরে আমরা দু ভাই-বোন প্রতিবছরই যেতাম সেই বৈশাখী মেলায়। বাবা না যেতে পারলেও পাঠিয়ে দিতেন বড় কারো সঙ্গে। আমাদের দু’জনের হাতে দেয়া হত একটি করে টাকা পুতুল বা যা খুশি তা কেনার জন্য। সেই সঙ্গে মিলত মাটির বটুয়ায় জমানো আমাদের ক্ষুদ্র সঞ্চয়।মা’র নিষেধাজ্ঞা ছিল বাইরের খাবার না কেনার জন্য। কিন্তু কে শোনে কার কথা? মেলার ধূলিমিশ্রিত নকুল দানা, কিংবা চৌকো করে কাটা তিলের খাজা, অথবা ঝুরঝুরে ঝুরিভাজার স্বর্গীয় স্বাদ কি ঘরের বানানো খাবারে হয়? সুতরাং মায়ের নিষেধাজ্ঞা তত্ত্বেই থাকত, বাস্তবে নয়।
মেলায় গিয়ে পড়তে হত এক কঠিন সমস্যায়। এত সব সুন্দর সুন্দর মাটির পুতুল – ঘোড়া, বর-বৌ, গরু, হাতী, পাখী – কোনটা ছেড়ে কোনটা নেই। পোড়ামাটির ওপরে সুন্দর উজ্জ্বল রংয়ে চোখ-মুখ আঁকা ঐ সব পুতুলদের দিকে তৃষিত নয়নে তাকিয়ে থাকতাম। মনে হত, দু’হাতে আঁকড়ে ধরে সব পুতুল নিয়ে নেই – কিন্তু সাধ আর সাধ্যে যে বিরাট ফারাক।তারই মধ্যে ছোট্ট মাথা খাটিয়ে পছন্দ করতাম কিছু পুতুল। কুমোরেরা যখন তাঁদের ডালি থেকে পুতুলগুলো আমাদের কচি হাতে তুলে দিতেন, তখন মনে হত, হাতে স্বর্গ পাওয়া গেল।
বাড়ী ফিরে সেই সব ঘোড়া, হাতীআর পাখীদের উল্টে-পাল্টে কতবার যে দেখা হত। রাতে ঘুমোনো হত ঐ সব পুতুলদের বালিশের পাশে সাজিয়ে।দু’টো ঘটনার কথা মনে আছে। একবার নিজের সঞ্চয় থেকে মা’য়ের জন্য একটা শিশু কোলে মা-পুতুল নিয়ে এসেছিলাম। সেদিন মায়ের মুখে যে খুশীর আভা দেখেছিলাম, তা কখনও ভুলব না। আর একবার আমার হাত থেকে আমার ঘোড়া পুতুলটা ভেঙ্গে গিয়েছিল। আমার মলিন মুখের দিকে তাকিয়ে আমার বোন তার ঘোড়াটা আমাকে দিয়ে দিয়েছিল। তার মূল্য তখন হয়তো বুঝিনি, আজ বুঝি।
সন্ধ্যের দিকে আবার শুরু হত আরেক পালা -হাল খাতা। বাবা আমাকে নিয়ে বেরুতেন মাখন কাকা আর হারধন জেঠার বইয়ের দোকানে, জহুর চাচার কাপড়ের প্রতিষ্ঠান, ‘চিটাগং বস্ত্রালয়ে, অশ্বিনীদা’র কাঠের কারখানায়। সুবেশ বিপনী মালিকেরা আমাদের যত্ন করে বসাতেন, সুস্বাদু সব খাবার আসত। তাকিয়ে দেখতাম লাল রংয়ের নতুন হালখাতা। যতদূর মনে পড়ে বাবা একটা টাকা প্রতীকি হিসেবে তাঁদের হাতে তুলে দিতেন।
সেই সব কর্মকান্ডে আমার যে কি যত্ন-আত্তি! কাকা-দাদারা হাঁক দিচ্ছেন তাঁদের কর্মচারীদের গরম গরম রসালো মিষ্টান্ন আনার জন্য, পরম যত্নে তুলে দিচ্ছেন আমার পাতে, জোর করছেন এটা ওটা খাবার জন্য। তারই ফাঁকে ফাঁকে বাবার কাছে আশীর্বাদ চাইছেন যাতে সারা বছরটা ভালো যায়। খাবার শেষে পেতলের ঘটি-গেলাশে জল আসত, বাবা একটা পান তুলে নিতেন হাতে, বিপনী মালিকেরা দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতেন।
কিন্তু সব সময়ে যা আমার দৃষ্টি কাড়ত, তা’হচ্ছে ঐ হালখাতা। সাদা সুতোয় বাঁধা লাল খাতাটা এলিয়ে থাকত টাকা-পয়সার বাক্সের পাশে। অদূরেই পেতলের ঘটিতে জলে পাঁচটি আমপাতা মুখ উঁচিয়ে থাকত। তার পাশেই কলম আর দোয়াত হিসেব লেখার জন্য। আমি প্রায়শ:ই ঐ লাল খাতাটির ওপরে হাত বুলোতাম। লালসালুর ঐ খাতাটি দেখতে দেখতে কেমন যেন ঘোর লেগে যেত।
তারপর সন্ধ্যা ঘন হয়ে আসত। বাড়ীর সামনে রিক্সা থেকে নেমে চোখে পড়ত, পাশের বাড়ীর বন্দনা মাসীমা ওঁদের উঠোনের মাঝখানে তুলসীতলায় দাঁড়িয়ে।সামনে মাটির প্রদীপ জ্বলছে আর তার আভায় সিঁদুর রাঙ্গা সিঁথি আর জ্বলজ্বলে টিপে মাসীমাকে দেবীর মতো মনে হতো। তাঁর গলায় জড়ানো লাল-সাদা শাড়ীর আঁচলে আর তাঁর নিমগ্নতায় কি যে সুন্দর লাগত তাঁকে। বাবা খুব নরম করে বলতেন, ‘যাও, মাসীকে প্রনাম করে এসো।’
আমি ওঁদের উঠোনের দিকে যেতে যেতে মনে হত, কাল রাতে আমার ঘরের জানালা থেকে দেখেছি, বন্দনা মাসী তাঁদের তুলসীতলা নিকিয়েছেন, বারান্দায় আলপনা এঁকেছেন চালের গুঁড়োর, মঙ্গলঘট বসিয়েছেন সিঁড়ির দু’ধারে।আজ খুব ভোরে ঘুমচোখে দেখেছি, ওঁদের বাড়ীর পেছনের ছোট্ট পুকুরটা একডুবে পার হয়ে ওপাড়ের ছোট্ট আমগাছটা থেকে দু’টো কচি আম তুলে আবার একডুবে ফিরে এসেছেন এ পাড়ের ঘাটে।
আমার পায়ের সাড়া পেয়ে বন্দনা মাসীমার তন্ময়তা ভেঙ্গে যেত।আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে বলতেন, ‘কি রে, বাবার সঙ্গে গিয়ে পেটপূজো সেরে এলি’? আমি কিছু না বলে বন্দনা মাসীমার পায়ের কাছে প্রনত হই। টের পেতাম, মাসীমার স্নেহময় হাত আমার পিঠে। আজ মনে হয়, ঐ আশীর্বাদ, ঐ মমতা আর মায়াই তো ঘিরে রেখেছে আমাকে – শুধু বছরের প্রথম দিনে নয়, সারা বছর এবং সারা জীবনও বটে।
সেলিম জাহান
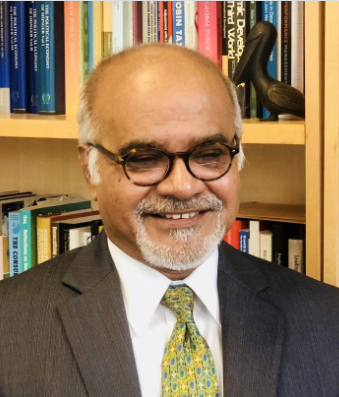
ড: জাহান লেখালেখি করছেন গত চার দশক ধরে। আশির দশকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এ সাময়িকীতে নিয়মিত লিখেছেন। রেডিও ও টেলিভিশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জননন্দিত উপস্হাপক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ১৯৯১-৯২ সালে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির মহাসচিব ছিলেন।ইংরেজী ও বাংলায় তাঁর প্রকাশিত গ্রণ্হের সংখ্যা এত ডজন এবং প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা দেড় শতাধিক। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্হ: বেলা-অবেলার কথা, স্বল্প কথার গল্প, পরানের অতল গহিণে, শার্সিতে স্বদেশের মুখ, অর্থনীতি-কড়চা, বাংলাদেশের রাজনৈতিক-অর্থনীতি, Overcoming Human Poverty, Freedom for Choice, Development and Deprivation.
এই লেখাটি সর্বমোট 87 বার পঠিত হয়েছে । আজকে 1 জন লেখাটি পড়েছে ।

