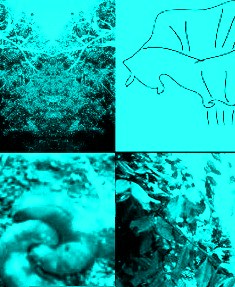পাপড়ি রহমান
আমি খুব আস্তে করে বলি–
‘ও দিদি ছোরমান নাকি চুরি করে খায়?’
দিদি পান খাওয়া লাল জিব দাঁতে কেটে বলে–
‘ধুর এইসব পোলাপানগো কথা শুনতে হয়না’
‘কিন্তু বেবাকে তো কয় ওরা চুরি করে?’
‘আরে ছোরমান না ওর ছোডুভাই চিকা চুরি করে। তাওতো গেরামে করে না। চুরি করে সে হাঁটে-বাজারে। হাঁটে যাইয়া সে মাইনষের পকেট মারে।‘
‘ও দিদি পকেট মারা কি?’
দিদি শাকের বোঝা ফেলে দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু পকেট মারার কোনো ব্যাখ্যা সে আমাকে দেয় না! বরং সামান্য ঘুরিয়ে অন্য কথা বলে–
‘বুঝলি না মাইনষের অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়’
দিদির কথা সত্য। ছোরমানদের যে অভাব আছে তা আমি যেমন জানি, গ্রামের সবাই তেমন জানে। আমি কতদিন দেখি আমাদের পুকুরে ছোরমানের বউ গোসল করে। তার একটাই শাড়ি। গলা পানিতে নেমে উদোম হয়ে রোজ সে তার শাড়িটা ধোয়। অর্ধেক শাড়ি গায়ে দিয়ে বাকিটা রোদে শুকায়। শুকনা অর্ধেক পরে ফের ভেজা অর্ধেক শুকায়। এমন করে কাপড় শুকানোর সময় তার লজ্জা-টজ্জা প্রায়ই কেউ না কেউ দেখে ফেলে। আমিও কতদিন দেখেছি। ছোরমানের বউয়ের পরনে কোনো সায়া নাই। তার লজ্জা-টজ্জার উপর বড় একটা তিল আছে তাওতো আমি কতদিনই দেখেছি। তার গায়ের একটাও ব্লাউজ নাই। আমার দিদির ব্লাউজ গায়ে দিলেই দম আটকে আসে বলে, সে উদলা গায়ে চলাফেরা করে। কিন্তু আম্মা-চাচী-ফুপুরা কেউ ব্লাউজ বিহীন চলার কথা ভাবতেই পারেনা।
আমাদের সাথে খেলতে আসে পান্না, আন্না, আঁখি- ওদের বড়চাচী এই ছোরমানের বউ। ওদের বাপ হলো চিকা, ওরফে চিকাচোর। খেলার সময় ভুলেও আমরা চিকাচোরের প্রসঙ্গ তুলিনা। আসলে ওদের বাপ যে চুরি করে এটা বলে আমরা ওদের লজ্জা দিতে চাইনা। আমরা ওদের নিয়ে খেলি কানামাছি, গোল্লাছুট, বউছি, দড়িলাফ, ইচিংবিচিং, ঝুক্কুর ঝুক্কুর মমিসিং এইসব কত কি!
আব্বা-চাচাজান ছুটিতে বাড়ি এলে অন্য দৃশ্য। গ্রামের গেরস্তরা বেশ সংকুচিত হয়ে আমাদের বাড়ির উপর দিয়ে হেঁটে যায়। আমাদের বাড়ির উপর দিয়ে যাওয়া ছাড়া ওদের আর কোনো উপায়ও নাই। পেছনের বাড়ির যে যেভাবেই যাবে তাকে সওদাগরবাড়ির আঙিনা দিয়েই যেতে হবে।
আব্বা বাড়িতে থাকলে চিকাচোর বেশ সম্ভ্রমের সাথে চলাফেরা করে। আব্বা চিকাচোরকে ডাকে মামু। চিকাচোরও আব্বাকে বলে মামু। আব্বা ক্যাপস্ট্যান সিগারেট খায়। সিগারেটে সুখ টান দিয়ে চিকাচোরকে ডেকে বলে– ‘মামু কিবা আছো?’
চিকাচোর লাজুকভাবে বলে– ‘আছি মামু ভালাই আছি। আপনে কিবা আছুন?’
আব্বা একশলা সিগারেট এগিয়ে দিলে চিকাচোর যেন আরো সংকুচিত হয়ে ওঠে। হাত সামান্য এগিয়ে সিগারেটটা হাতে নিয়ে বলে– ‘মামু এত দামেরডা খাইলে যে বদভ্যাস হইয়া যাবো’
আব্বা হো হো করে হেসে বলে–
‘আরে খাও মামু খাও-একটা দুইডা খাইলে কি আর এমুন অভ্যাস বদভ্যাস হইয়া যাইব?’
চিকাচোরকে আব্বা ম্যাচ দিলে সে বেশ প্রশান্ত মুখে সিগারেট ধরায়।
চিকাচোর চোর হলে কি হবে, তার নীতিজ্ঞান বেশ প্রখর। সে নিজ গ্রামের কারো বাড়িতে চুরিধারি করে না। সিঁধ কাটে না। তার যত হাত সাফাই চলে অচেনা গ্রামে। হাটের অচেনা মানুষের পকেটে। হাটুরেরা যারা হাটে আসে তাদের পকেট খালি করে সে নিজের পকেট ভরতি করে।
তবে চিকাচোরের যেমতি হ্যাঙলা-পাতলা দেহ, তাতে সে যে কিভাবে চুরি করে তা আমার মাথায় ঢোকে না। এমন ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে চুরি করার সাহস সে কিভাবে পায়? তখন হয়তো সামান্য সামান্য বুঝতে শিখছি আমি। দুই-একজন মানুষের মুখ চিনতে শিখছি। একেবার সুপারি গাছের মতো সরু মানুষটা কিভাবে মানুষের পকেট কাটে? কেন সে চুরি করে? অন্য কাজ করলে তার সমস্যা কি?
একদিন বিষ্যুদবার হাটের বেলা প্রায় যাই যাই করছে- এমন সময়ে ময়নার মা বিলাপ করতে করতে ছুটতে শুরু করলো আমাদের বাইরবাড়ি দিয়ে–
‘ও আল্লারে, আমার এমুন সব্বোনাশ কেমনে হোইল রে!’
ময়নার মা বিলাপ করে ছুটছে আর তার পিছু পিছু ছুটছে ময়না, পাখি, আন্না, পান্না, আঁখি, বড়গেদা, ছোটগেদা, আকাইল্যা ওদের সব ছেলেমেয়ে।
এতজনের সন্মিলিত কান্না আর চিল্লাচিল্লিতে আমরা বাড়ির প্রায় সকলেই খালপারে।
ঘটনা কি?
চিকাচোর যেন কার পকেটে হাত দিয়ে ধরা খেয়েছে! আর হাটুরেদের গণপিটুনিতে তার দফা রফা হলো বলে।
আমাদের খালে তখন কোমর সমান পানি। ময়নার মার কোনোদিকে ভ্রক্ষেপ নাই! সে পাছা উদাম করে খাল পার হয়ে গেল! এদিকে তাদের এক দঙ্গল ছেলেমেয়ের মরা কান্নার বিরাম নাই। আমরা হা করে তাকিয়ে তামশা দেখছি। প্রায় ঘন্টা দেড়েক পরে চিকাচোরকে পাঁজাকোলে করে নিয়ে সকলে ফিরে এলো। চিকাচোরের চোখ-মুখ রক্তাক্ত। হাটুরেদের কেউ একজন আঙুল দিয়ে তার বাম চোখটা উপড়ে নেয়ার চেষ্টা করেছে। একেবারে কঞ্চির মতো শুকনা লোকটাকে ময়ানার মা একাই খাল পার করে নিয়ে এলো। ছেলেমেয়েরা তখনো বিলাপ করছে! মারত্নক রক্তারক্তি মানুষ আমি এই প্রথম দেখলাম। প্রচণ্ড ভয়ে আমার বুক কাঁপতে লাগলো। আমাদের বাড়ির কেউ কোনো কথা বলছে না! পান্নাদের কান্না দেখে আমারও বেদম কান্না পেল। ওরা আমার প্রতিদিনের খেলার সাথি, বাপের চুরির খেসারত ওদেরও দিতে হচ্ছে দেখে আমিও কাঁদতে লাগলাম।
সে যাত্রায় চিকাচোর প্রায় ছয়মাস ঘরে শয্যাশায়ী ছিল। এবং ভালো হয়ে পুনরায় ফিরে গিয়েছিল তার পুরাতন পেশায়!
জলে ভাসা কোষা
বাইস্যা মাস এলে ভজঘটের শেষ নাই। উইন্যা মাসে আমরা যেখানে কুম্ভীর কুম্ভীর খেলি, বর্ষায় সেখানে তুখা স্রোত। খালটা যেন পলকেই নদী নাকি সমুদ্দুর হয়ে ওঠে! তখন পারাপারে এমন অসুবিধা! মসজিদ-বাজার-হাট-ঘাট যা-ই কিছু করনা কেন খাল পেরোতেই হবে। খালও আবার যেই সেই খাল নয়-বিশাল চিতলের পেটির মতো চওড়া খাল!
বানের পানি খালে প্রথম ঢুকা মাত্রই শুরু হয়ে যায় চাচাদের ব্যস্ততা। বাঁশের ছোপ থেকে তখন তারা বাঁশ কাটবে, তাতে দড়ি বাঁধবে আর পুল বানাবে। একবাঁশের পুল। যাতে পা দেয়া মাত্রই ভয়ে পায়ের তালু শিরশির করে ওঠে! উঠবে না? নিচে তাকালেই তো তুখা স্রোত। মনে হয় পানির তলার চুল প্যাঁচানিটা ঠিক পুলের নিচেই তার চুল প্যাঁচিয়ে ঘুর্ণি তুলছে! সেই ঘুর্ণিতে পড়ে ভেসে যাচ্ছে কলমির ডগা, বেগুনি-ফুল-ভরা দাম, শুকনা লাকড়ি, মরা বিড়াল বা কুকুর। কখনো সখনো মরা গরু পর্যন্ত। ওই পুল থেকে একবার পা ফসকাতে পারলে এতসব ভাসন্তের সাথে তুমিও দিব্যি ভেসে যাবে। আর বাপু যদি সাঁতার না জানো তাহলে নির্ঘাত ডুবে মরবে। বাড়ির চাচারা পুলের সাথে পেরে না উঠলে দাদাজানকে দেখি কামলা ডেকে আনে। কামলা এলে একবাঁশের পুলসিরাত দুইবাঁশের পুল হয়ে যায়। ফলে দুই বাঁশের পুলে পা ফেলতে অত আর ভয় করে না।
এক বর্ষায় দেখি চির পুরাতন দৃশ্য বদলে গেল! দাদাজান কামলার বদলে ছুঁতার ডেকে নিয়ে এলো। ছুঁতার দেখে আমাদের বিস্ময়ের শেষ নাই-দাদাজান খাল পারাপারের জন্য এইবার কোষানাও বানাবেন।
অবশ্য নাও না বানিয়ে দাদাজানের উপায়ও নাই, তারতো ঘরভরা ঝুণ্ডিরপাল! আমাদের ঘরে এত বেশি পোলাপান দেখে অন্য ঘরের দাদী-চাচীরা আমাদের ডাকে ঝুণ্ডির পাল। দাদাজানের চার ছেলে দুই মেয়ে। বড়চাচা ইসমাঈল হোসেন সওদাগর- আমার চাচাজান, তার তিন ছেলে। মেজ আমার আব্বা, আবুল হোসেন সওদাগর- তার এক ছেলে আর এক মেয়ে। তিন নম্বর সেজ চাচা মুয়াজ্জেম হোসেন সওদাগর-বিয়ে থা হয় নাই। চার নম্বর ইফতে খারুল হামিদ- আমার চাইতে ছয়/সাত বছরের বড়। বড় মেয়ে রাশিদা বেগম- তার এক ছেলে ও স্বামীসহ আমাদের বাড়িতেই বেশির ভাগ থাকেন। ছোটমেয়ে আছুদা বেগম ওরফে রেহানা- বিয়ের লায়েক। তারমানে দাদাজানের একেবারে ভর-ভরন্ত সংসার। আমাদের ঘরে আমিই খালি একমাত্র কন্যা সন্তান আর সবাই পুত্র। আমাদের ঘরের সাতের সংগে যুক্ত হয় আব্বার অন্য চাচাতো ভাইবোনদের ছেলমেয়েরা। আরো আছে আমাদের ঘরে দুইজন কাজের ঝি। আসে চিকার বাড়ির ছেলেমেয়েরা। ফলে প্রায় বেশ বড় একটা দল ছুঁতারের কাজ দেখি।
দেখি বড় বড় কাঠের তক্তা কিভাবে রানদা করে মসৃণ করা হয়। কাঠপেন্সিল-স্কেলে মেপে কিভাবে বাটাল দিয়ে চেঁছে মাপ ঠিক করা হয়। কাঠের গতরে নিঁখুত ভাবে স্ক্রু-পেরেক মারা হয়। এইসব নাই-নুহুরি কাজকামেই ছুঁতার প্রায় শ্রাবণ মাস পার করে ফেললো। এদিকে আমাদের আর তর সয়না। কবে যে পানিতে ভাসবে আমাদের কোষানাও? আমাদের কাঠের কাজ যে মিস্ত্রি করে তার নাম পলান। কাঠের কাজে পলানের খুব নামডাক সারা গ্রামে। কিন্তু আমরা তো দেখছি- কাজ সে যা-ই করুক না কেন, আমাদের নাও বানাতে তার যেন কোনো ইচ্ছা নাই। নইলে তাড়াতাড়ি করছে না কেন? সে প্রতিদিনই পোটলায় করে শুকনা চিঁড়া/গুঁড় নিয়ে আসে। সাথে একটা বাসন, একটা গ্লাস। সেই বাসনে সে ধীরসুস্থে চিঁড়া ভেজায়। চিঁড়া ভিজে উঠলে গুঁড় মেখে রসিয়ে রসিয়ে খেয়ে বিড়ি ধরায়। আর চোখ বুঁজে বুঁজে বিড়িতে টান দেয়। গা মোচরামুচরি দিয়ে ফের রানদা করতে বসে। আশ্চর্য! আমরা কোষার জন্য তীর্থের কাকের মতো বসে আছি-সে আমাদের পাত্তাই দেয় না! এদিকে খালের পানি আষাঢ়ের মেঘের মতো ফুলে উঠছে। আমরা মনে মনে রেগেমেগে কাঁই হয়ে যাই– ‘শালার বেটা, মুসলমানের ছোঁয়া খাইলে তোমার জাত যায়, একটা নাও বানাইতে তোমার কতদিন লাগে? অ্যাঁ? নাওযে বানাইতেছ সেইটায় কেরা চড়বো? তোমার জাত খাওয়া মুসলমানই তো নাকি? তখন তোমার জাত থাকবো কই? আর এই যে জলে চিঁড়া ধুঁইয়া খাও সেটা তো মুসলমান বাড়িরই নাকি?’
আমরা যে ক্রমান্বয়ে অসহিঞ্চু হয়ে উঠছি এটা হয়তো পলান মিস্ত্রী টের পায়। ফলে একদিন ঘুম থেকে জেগে দেখি আমাদের নাও বাঁশের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে আমরা আনন্দে হইচই করে উঠি।
দাদাজান নাওয়ের গলুই কাঠের বদলে টিন দিয়ে মুড়ে দিতে বলে। আর পলান মিস্ত্রীও তাই করে। ওই গলুইয়ের টিনের উপর রোদ্দুর পড়ে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। কিন্তু দাদাজান নাও ভাসানের কথা কিছুতেই মুখে আনে না। আমাদের ভীষণ ভাবে উছপিছ লাগে। দাদাজানের পিছু পিছু ঘুরাঘুরি করে জানতে পারি নাওয়ে গাবের রস দিয়ে তবেই তা পানিতে নামানো হবে। গাবের রসের প্রলেপ না দিলে নাওয়ের কাঠ নাকি পানি দ্রুত খেয়ে যাবে। লে হালুয়া, আমাদের খুশি সুতা কাটা ঘুড়ির মতো গোত্তা খেয়ে খেয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে।
অবশ্য চিন্তার বেশি কিছু নাই, আমাদের বাড়ির শেষ সীমানায় যে ভুতুড়ে গাবগাছ সেটা থাকতে গাবের রসের জন্য আর চিন্তা কি? এবং ঠিক তাই হয়, চাচাদের দেখি তেমন ভয়ডর নাই-তারা ওই ভুতুড়ে গাছে চড়ে ঝাঁকাকে ঝাঁকা গাব পেড়ে আনে। সেই গাব ঢেঁকিতে গাড়ুম গুড়ুম করে পাঁড় দিয়ে বালতির পানিতে তিন-চারদিন ভিজিয়ে রাখা হয়। তারপরে সেই গাবের রসের পোঁচ দেয়া হয় নাওয়ের গতরে। কিন্তু ঝামেলা যা ঘটার ঘটে যায়। আমাদের সুন্দর কোষা তার শ্রী হারায়। বিশ্রী রকম কালসিটে হোয়ে ওঠে তার বাদামী শরীর।
অপেক্ষা করে করে আমরা ক্লান্তি বোধ করি। টানা সাতদিন রোদের নিচে ফেলে রাখার পর শ্রী হারানো কোষা জলে ভাসে! আমার ছোটকা, চাচাতো ভাইয়েরা বৈঠা নিয়ে উল্লাস করে। তারা বৈঠা বেয়ে খাল পেরিয়ে পাটক্ষেতের ভেতর দিয়ে কোন বিলে নাকি খালে চলে যায়। তারা নাও বোঝাই করে নিয়ে আসে শাপলা, শালুক, ঢ্যাপ। তুলে আনে কলমিশাক। দিদি বলে, ‘এই যে পোলাপান লালরঙা ঢ্যাপ খাইও না , অইগুলায় সাপের বিষ থাকে।‘
আমরা শাপলা ফুলের ভেতরের রেনু খেয়ে ঠোঁট হলুদ করে ফেলি। কালোরঙের ঢ্যাপ খেতে খেতে পেট ভরিয়ে ফেলি। ভাইদের সাথে কোষায় চড়ে পানির উপর হাঁসের মতো ভাসতে থাকি। আর তুলে আমি গাঙকলা। গাঙকলার বিজলা-নোনতা স্বাদে আমার জিব-ঠোঁট ভরে থাকে…
এই লেখাটি সর্বমোট 762 বার পঠিত হয়েছে । আজকে 1 জন লেখাটি পড়েছে ।